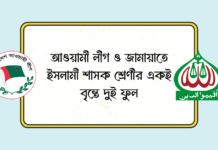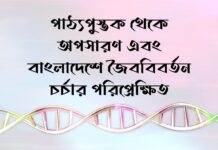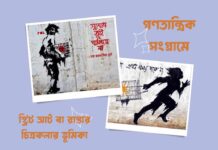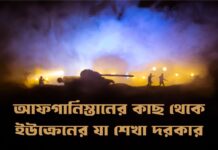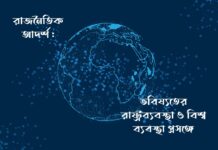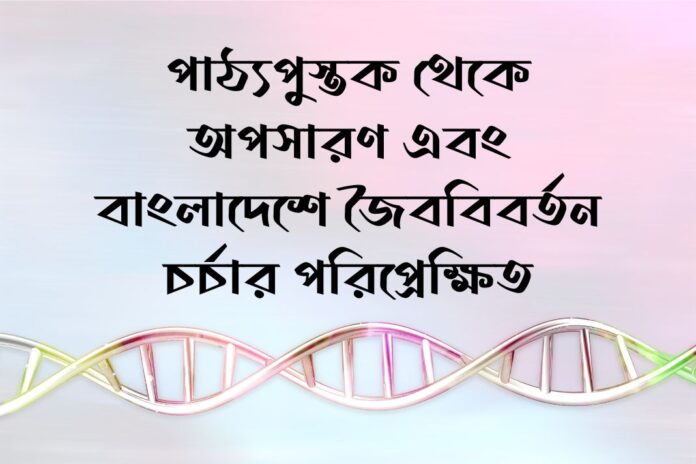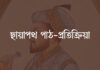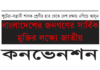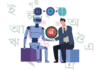স্পেশাল ক্রিয়েশনের কবলে শিক্ষাব্যবস্থা
এ বছরের শুরুতে বিদ্যালয়ের নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণের পর থেকেই পাঠ্যক্রম নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্কের সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয় ছিল ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষাক্রমে জৈববিবর্তনকে অন্তর্ভূক্ত করা নিয়ে। ইসলামী কিছু দল ও গোষ্ঠি এর বিরোধিতা করে কিছু তৎপরতা দেখানোর পর সরকারী নির্দেশে পাঠ্যপুস্তক থেকে ঐ অংশটি বাদ দেয়া হয়েছে। যদিও সম্প্রতি তুরস্কের ইসলামপন্থী এরদোগান সরকারও সেদেশের নবম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম থেকে জৈববিবর্তনের অংশটি বাদ দিয়েছে কিন্তু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানসহ বেশিরভাগ মুসলিম-প্রধান দেশে জৈববিবর্তন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত আছে। এর কারণ আধুনিক যুগে জৈববিবর্তন কেবল জীবের উৎপত্তি ও বিকাশের তত্ত্ব নয় এটি জীবজগতের গতি-প্রকৃতিকে বোঝার মূল সোপান। এ জন্য একে বলা হয় ‘জৈব-অভিব্যক্তি’। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বাদ দিয়ে জীববিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানচর্চার গভীরে যাওয়া সম্ভব নয়। জীবের বিবর্তন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত একটি সত্য। ডারউইনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই তত্ত্ব এতটাই সমৃদ্ধ হয়েছে যে প্রতিটি প্রজাতির উৎপত্তি, বিকাশ ও তাদের অস্তিত্ত্বের ভবিষ্যত সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে এই জৈববিবর্তনের জ্ঞান। অথচ এই তত্ত্ব ‘প্রমাণিত নয়’ এই ‘যুক্তিতে’ এদেশের ধর্মান্ধ গোষ্ঠি এর বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে জৈববিবর্তনকে বাদ দেবার ঘটনা অবশ্য এবারই প্রথম নয় আগেও একবার এমন ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে আমরা পরে আসছি।
প্রায় একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন “…পৃথিবীতে আর সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ, আর সকল দেশের বিদ্যা বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ভ্রম কাটাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা শিবের প্রসাদে এক মুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ভ্রমলেশ বর্জিত হইয়া অনন্ত কালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন ইহা তাই, ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহা ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত…ইহাকে কেবল বিশ্বাসের দ্বারা বহন করিতে হইবে, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে না।” বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এখানে জীবের ক্ষেত্রে সৃষ্টিবাদীদের ‘স্পেশাল ক্রিয়েশন’কে ধিক্কার জানাননি কিংবা জীবের ক্রমবিকাশের কথাও বলতে চাননি, তুলনা দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু দু’দিক থেকে এই উক্তি আমাদের বর্তমান আলোচনায় খুব প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হন বা না-ই হন বিংশ শতাব্দীতে কোনো যৌক্তিক মানুষের পক্ষে ‘স্পেশাল ক্রিয়েশনে’ আস্থা রাখা সম্ভব নয় এবং একইভাবে প্রতিটি প্রপঞ্চের ক্ষেত্রেই যে ক্রমবিকাশ ঘটে সে সত্যকেও মেনে নিতে হয়। এই উক্তিটির এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, একশো বছর পরেও সেই বাস্তবতার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আমাদের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে যেমন ক্রমবিকাশ নগণ্য, তেমনি জগতের ক্রমবিকাশকে জানবার এবং বুঝবার প্রবণতাও এই চর্চার মধ্যে অতি সামান্য। এর মধ্যে জীবনের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব জৈববিবর্তনের চর্চা রয়েছে সবার পেছনে, কারণ এর বিরুদ্ধে রয়েছেন অনেকেই, যাঁরা জগৎকে ‘ভ্রমলেশ বিবর্জিত’ অনড় বস্তু বলে মনে করেন। এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রয়োগ করলেও জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশের ক্ষেত্রকে ‘কেবল বিশ্বাসের দ্বারা বহন’ করতে চান। এদের সামাজিক ও রাজনৈতিক শেকড়ের গভীরতার সাথে সমানুপাতিক হারে বাড়ছে সমাজে জৈববিবর্তন সম্পর্কে অস্পষ্টতার ধূম্রজাল এবং মুক্তচিন্তা বিকাশের প্রতিবন্ধকতা। এই বাস্তবতার মধ্যেই দেখতে হবে এদেশে জৈববিবর্তন চর্চার পরিপ্রেক্ষিতকে।
শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার মূল উদ্দেশ্য দুটি- প্রথমত, জগৎকে বুঝতে শেখা এবং একে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা। ধারাবাহিক বিকাশের মধ্য থেকে না দেখলে জগতের কোনো প্রপঞ্চ সম্পর্কেই একটি পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা জীবজগতের অংশ এবং জৈব পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই বাস করি। অতএব, জীবের উৎপাত্তি ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘটে এবং এই বিকাশের নিয়ম কী কী তা জানা জগৎকে বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য অপরিহার্য। খাদ্য, বস্ত্রসহ মানুষের অধিকাংশ প্রয়োজন মেটে জীবজগৎ থেকে। আমাদের টিকে থাকার ক্ষেত্রে অনেক হুমকিও আসে জীবজগৎ থেকেই। অতএব, জীবজগৎ থেকে উত্তরোত্তর আনুকূল্য অর্জন এবং প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজনে জৈববিবর্তনের বোধ মানুষের জাগতিক বোধের অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ হয়ে ওঠে। জৈববির্বতন সম্পর্কে জানা বা বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানের চর্চা তাই কেবল বিজ্ঞানের একটি শাখা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা নয়, বরং প্রকৃতি জগতের ক্রিয়াকলাপ এবং এর পরিবর্তনের নিয়মকে বোঝার ক্ষেত্রে অপরিহার্য একটি ভিত্তি। বিদ্যাচর্চার সাথে সম্পর্কিত এ দেশের মানুষদের অধিকাংশই জৈববিবর্তনের এই গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নন।
ব্যাপ্তি এবং জটিলতার দিক থেকে গভীর এ বিষয়ের চর্চা করা অগ্রসর ও কৌতূহলী মনের পক্ষেই সম্ভব। আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকাঠামোর মধ্যে সংকুচিত হতে থাকে শিক্ষার্থীদের কৌতূহলী মন, মনন ও সৃজনশীলতা। বিদ্যাচর্চা এখানে কোনো গভীর মননশীল বিষয়কে উপজীব্য করতে পারে না। এই কাঠামোর মধ্যে জৈববিবর্তনের তত্ত্ব বা এরকম কোনো গভীর বিষয়ের চর্চা টিকিয়ে রাখা কঠিন। আমাদের দৃশ্যমান জগতের অধিকাংশ বিষয়েরই একটি জীবতাত্ত্বিক মাত্রা রয়েছে, যার উৎপত্তি ও বিকাশকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে গেলে প্রয়োজন জৈববিবর্তনের জ্ঞান। অতএব, যে আকাঙ্ক্ষা ও সংশয় নিয়ে আমরা আজ জৈববিবর্তন চর্চার পরিপ্রেক্ষিতকে মূল্যায়ন করতে বসেছি তা হলো, কী করে এদেশের এই প্রতিকূল পরিবেশে আমরা এর চর্চা চালিয়ে যাব?
চর্চার দৈন্য এবং বিরোধিতার জাঁকজমক
বাংলাদেশে জৈববিবর্তনের চর্চার চেয়ে বিরোধিতার চর্চা বেশি বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। চর্চার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাঠ্যপুস্তক, সৃজনশীল বই, পত্রপত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং বিকল্প শিক্ষার সংগঠন, যেমন-পাঠচক্র, অধ্যয়নচক্র, সেমিনার, আলোচনাসভা ইত্যাদি। এর মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পাঠ্যপুস্তকে এই চর্চা এবং বিরোধিতার চর্চা সম্পর্কে আমরা একটু পড়ে আলোচনা করব। অন্য মাধ্যমগুলোর মধ্যে বই বেশ গুরুত্বপূর্ণ।
একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে জৈববিবর্তন সম্পর্কে এদেশে যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ের বই লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ লেখকই একাডেমিক জীবনে অন্য বিষয়ের ছাত্র। তবে সে কারণে বইগুলোর মান কমে যায়নি। বইগুলো যথেষ্ট তথ্যবহুল, বস্তুনিষ্ঠ এবং সুলিখিত। কিন্তু দু-একটি ছাড়া প্রায় সবগুলো বই সাধারণ পাঠকের কাছে জৈববিবর্তনের বিভিন্ন দিককে পরিচিত করানোর জন্য লেখা হয়েছে। জৈববিবর্তন তত্ত্বের ইতিহাস, তত্ত্বের সহজ উপস্থাপনা, বিতর্কগুলোর পরিচয়, বিরোধিতার স্বরূপ এবং এই তত্ত্ব গ্রহণের সংকট ইত্যাদি বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে এসব বইয়ে। সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু কিছু বইয়ে উঠে এসেছে আধুনিক বংশগতিবিদ্যার আবিষ্কার কিভাবে জৈববিবর্তন তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে এবং জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞান যেসব নতুন নতুন তথ্য দিচ্ছে।
জীবনের এবং পরিবেশের নানা দিকের জীবতাত্ত্বিক মাত্রাকে বোঝার ক্ষেত্রে জৈব বিবর্তনের প্রয়োগ, কিংবা জৈব বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক-দার্শনিক অনুষঙ্গকে তুলে আনে, জৈববিবর্তন ভিত্তিক এ ধরনের গভীর এবং বিস্তৃত পরিসরে বাংলা ভাষায় লেখা উল্লেখযোগ্য বই বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি। এ পর্যায়ের বইয়ের পাঠক এই জনপদে নেই তা নয়। কারণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এসব বিষয়ে লেখা বিভিন্ন লেখকের বই এদেশে একেবারে পঠিত হয় না তা কিন্তু নয়। এদেশে জৈব বিবর্তনের বই সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ আছে। যদিও বেশির ভাগ পাঠকই প্রারম্ভিক বা দ্বিতীয় পর্যায়ের। উচ্চতর পর্যায়ের পাঠকের সংখ্যা কম হলেও নগণ্য নয়। তবে তাঁদের কাছে এ ধরনের লেখা পৌঁছচ্ছে না, কারণ এ পর্যায়ের দেশীয় লেখা নেই বললেই চলে এবং বিদেশি লেখাগুলো বহুল প্রচারিত এবং সহজলভ্য নয়। উচ্চতর পর্যায়ের লেখাগুলো কম হবার একটি প্রধান কারণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানের পাঠ ও গবেষণার অপ্রতুলতা।
নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, আচরণবিজ্ঞান, মানুষের বুদ্ধিমত্তা, লিঙ্গবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, কৃষিপ্রযুক্তি, পরিবেশবিজ্ঞান ইত্যাদি অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রেই জৈবিক মাত্রা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই বিষয়সমূহের জৈবিক দিকটি এবং এদের উৎপত্তি ও পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতিকে বোঝার ক্ষেত্রে জৈব বিবর্তনের জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু যেহেতু উক্ত বিষয়গুলোর চর্চার ক্ষেত্রে জৈবিক মাত্রাকে গভীরভাবে জানার প্রবণতা কম, তাই এসব বিষয়ের চর্চার ক্ষেত্রে জৈব বিবর্তনের জ্ঞানের প্রয়োগ ও অধ্যয়ন নেই বললেই চলে।
সিমন দ্য বুভোয়া তাঁর সেকেন্ড সেক্স বইয়ে লিঙ্গবৈষম্যকে গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছেন। তাই তাঁর বইয়ের শুরুতেই লিঙ্গবিভেদের জীববিজ্ঞানিক মাত্রাকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর এই প্রচেষ্টার মধ্যে জৈববিবর্তনের জ্ঞানের প্রয়োগ লিঙ্গবৈষম্যের বিভিন্ন দিকের উৎপত্তি ও বিকাশকে বুঝতে সহায়তা করেছে। এ যুগের আধুনিক চিন্তাবিদদের অনেকেই সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক অনেক বিষয়কে বোঝার ক্ষেত্রে জৈববিবর্তনের জ্ঞানকে প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন প্রপঞ্চের জৈবিক মাত্রাকে বোঝার ক্ষেত্রে জৈববিবর্তনের জ্ঞান যে অপরিহার্য, তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ধারার লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জুলিয়ান হাক্সলি, জে বি এস হলডেন, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, জে ব্রনোওস্কি, এডওয়ার্ড উইলসন, স্টিফেন জে গুল্ড এবং আরও অনেকে। বাংলাদেশে বা বাংলা ভাষায় এ ধারাকে সমৃদ্ধ করার মতো শক্তিশালী কোনো লেখক আমরা এখনও পাইনি।
ছাপানো মাধ্যমের মধ্যে বই ছাড়াও পত্রপত্রিকা ও ছোট কাগজে জৈববিবর্তন সম্পর্কিত লেখা ছাপা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন পাঠচক্র এবং অধ্যয়নচক্রে জৈববিবর্তন এবং এ সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। এগুলো কোনো নিয়মিত ব্যাপার নয়। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে এদেশে সবচেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে টেলিভিশন। দেশীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে জৈববিবর্তন ভিত্তিক অনুষ্ঠান নেই বললেই চলে। তবে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে জৈব বিবর্তনের বিরোধিতার চর্চা একটি নিয়মিত ব্যাপার। ইসলামি টিভি এবং অন্যান্য বাংলা চ্যানেলের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জৈব বিবর্তনের বিরোধিতা করে নানা বক্তব্য দেয়া একটি নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।
পাঠ্যক্রমে জৈব বিবর্তন এবং ৫ জন শিক্ষকের গল্প
যে আশঙ্কা নিয়ে আমরা এ আলোচনা শুরু করেছিলাম তার সবচেয়ে গভীর দিক হচ্ছে পাঠ্যক্রমে আক্রমণ। জীববিজ্ঞানের সমন্বয়কারী ধারণা জৈববিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষার ভিত গড়ে ওঠার সময় থেকে সঠিকভাবে জানার গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত জৈববিবর্তন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত জীববিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর খুব নীরবে এটি পরবর্তী সংস্কারকৃত সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া হয়। নীরবে বলছি এই কারণে যে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তত্ত্বকে কী কারণে বাদ দেয়া হলো এবং এটি বাদ দেবার আগে এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের মতামত নেয়া হলো না কেন এসব কিছুই উল্লেখ করেনি নতুন সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি। এই পরিবর্তন নীরবেই করা হয়েছিল যাতে এ নিয়ে বেশি হৈ চৈ না হয়। এটা যাঁদেরই উদ্যোগে বা প্ররোচনায় হোক না কেন, এ ঘটনার পর এদেশের প্রগতিশীল এবং মুক্তচিন্তার ব্যক্তিদের নীরবতাও লক্ষণীয় একটি ব্যাপার। এই নীরবতার একটি কারণ হতে পারে ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা। কিন্তু বিষয়টি জানার পরও এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে তেমন কোনো জোরালো প্রতিক্রিয়া এবং তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি।
“যেদিন সার্ভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট-এই সাধারণ সত্যটি দার্শনিকের কণ্ঠে ঘোষিত হলো, সেদিন থেকেই পৃথিবীর সর্বনাশের সূত্রপাত।” এটি কোনো মৌলবাদী এবং বিজ্ঞানবিরোধী ব্যক্তির বক্তব্য নয়, এদেশের মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী পুরুষ মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর ‘মেরুদন্ড’ নামক প্রবন্ধে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে একথা লিখেছেন। বিষয়টা আমাদের কাছে একটু গোলমেলে মনে হলেও সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পড়লে আমরা বুঝতে পারি যে মোতাহের হোসেন চৌধুরী আসলে জৈববিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতা করছেন না, তিনি বিরোধিতা করছেন জৈববিবর্তন তত্ত্বের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট বহুল প্রচারিত সামাজিক ডারউইনবাদ (Social Darwinism) তত্ত্বের। প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা যে শুধু জীবজগতে সীমাবদ্ধ, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিরও তা জানা ছিল না। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো তাঁর জানা ছিল না তা হলো-১. জীববিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী (central unifying) চিন্তা হলো জৈববিবর্তন তত্ত্ব। ২. জীব এবং জৈবনিক ক্রিয়াকে গভীরভাবে বোঝার জন্য এই তত্ত্ব অপরিহার্য। এবং ৩. এই তত্ত্ব সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
অন্যান্য অনেক বিষয়ে পান্ডিত্য এবং গভীর চিন্তার অধিকারী হলেও জৈব বিবর্তন সম্পর্কে ভুল ও বিকৃত ধারণার অধিকারী তিনি কেন হলেন সেটাই ভাববার বিষয়। আসলে মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান বিষয়ক কোনো বই পড়েননি। তিনি জৈববিবর্তন সম্পর্কে জেনেছেন বার্নাড শ এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের লেখার মাধ্যমে। শ জৈব বিবর্তনের তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন এক ধরনের ভাববাদী আবেগ দিয়ে। তাঁর ভাষায় “If the wicked flourish and the fittest survive, Nature must be the God of rascals”। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর লেখায় আমরা এ ধারণার প্রতিফলনই দেখতে পাই। জৈববিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণার কোনো প্রতিফলন সেখানে নেই। তিনি যে সময় লেখাপড়া করেছেন, সে সময় জৈববিবর্তন তত্ত্ব যদি তাঁদের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকত এবং সুযোগ্য শিক্ষকের মাধ্যমে বিষয়টির চর্চা হতো, তাহলে তাঁর মতো গভীর চিন্তাশীল মানুষ তো বটেই, সাধারণ মানুষের মধ্যেও জৈববিবর্তন সম্পর্কে ভুল ধারণা অনেকটাই কেটে যেত।
পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকলেই জৈববিবর্তনের চর্চা খুব ভালোভাবে হচ্ছে তাও বলা যাবে না। তবে বিষয়টির সঠিক চর্চার জন্য পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা পর্যায়ে বিষয়টির গভীর ও বিস্তৃত চর্চা খুব প্রয়োজনীয়। নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত যখন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল তখনও অধিকাংশ কলেজেই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়নি। এর কারণ ছিল তিনটি-ক) এটি পড়ানোর মতো যোগ্য শিক্ষকের অভাব; খ) বিষয়টিকে গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা; গ) দার্শনিক কারণে এ তত্ত্ব পড়ানো ক্ষতিকর মনে করা।
আমি ব্যক্তিগতভাবে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে যে শিক্ষক পেয়েছিলাম তিনি ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য একজন শিক্ষক। তাঁকে যোগ্য বলছি দুই কারণে। তিনি বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতেন এবং দৃঢ় আস্থার সাথে আমাদের বলতে পেরেছিলেন যে জৈববিবর্তন সত্য ঘটনা, এ ব্যাপারে জীববিজ্ঞানীরা নিশ্চিত এবং জীবজগতের পরিবর্তনের নিয়ম হচ্ছে জৈববিবর্তন। এর পাশাপাশি ঢাকার একটি নামি কালেজের বিখ্যাত জীববিজ্ঞানের শিক্ষক (পাঠ্যবইয়ের প্রণেতা) ছাত্রদের বলতেন, এসব থিওরির জোরালো কোনো প্রমাণ নেই। পরীক্ষা পাসের জন্য পড়তে পারো। অর্থাৎ পাঠ্যক্রমে থাকলেই হবে না, বিষয়টি কিভাবে পড়ানো হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে যাঁরা উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে জৈববিবর্তন পড়েছেন তাঁদের অধিকাংশই বিষয়টি সম্পর্কে খুব গভীরভাবে জানেন না এবং এটাও জানেন না যে জৈববিবর্তন জৈবিক বিজ্ঞানসমূহের (biological sciences) অপরিহার্য একটি ভিত্তি। জীববিজ্ঞানের পেশাদার শিক্ষকদের কাছ থেকে যে ছাত্র জৈববিবর্তন সম্পর্কে নেতিবাচক এবং ভুল কথা শুনবে, এ বিষয়টি গভীরভাবে অধ্যয়ন করার বা অনুধাবন করার আগ্রহ সে হারিয়ে ফেলবে, সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।
এর বিপরীতে যদি পাঠ্যক্রমে বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং সুযোগ্য শিক্ষকগণ বিষয়টি পড়ান তাহলে ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাও বুঝতে পারেন এটি ভিত্তিহীন নয় এবং প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। আমেরিকার জোফারসনের জীববিজ্ঞানের এক শিক্ষক গোড়া খ্রিস্টান পরিবারে ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছেন। কিন্তু জৈববিবর্তনের তত্ত্ব অধ্যয়ন এবং গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ তিনি বুঝেছেন এই তত্ত্ব জীবজগতের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে, “কোন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম ঈশ্বরের সৃষ্টি।” অতএব, প্রাকৃতিক নিয়মে জীবজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এটি তাঁর বিশ্বাসের পরিপন্থী নয় বলে তিনি মনে করেন। একজন গোড়া ধার্মিক হয়েও এই ব্যক্তি যে জৈব বিবর্তনকে গ্রহণ করতে পেরেছেন তার পেছনে রয়েছে বিষয়টির সঠিক অধ্যয়ন, তাঁদের পাঠ্যক্রমে জৈববিবর্তনের উপস্থিতি এবং উপযুক্ত শিক্ষকের মাধ্যমে বিষয়টির গভীরে যেতে পারা। এর বিপরীতে ওই স্কুলের রসায়নের এক শিক্ষকের প্ররোচনায় উঁচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা জৈববিবর্তন পড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, কারণ তাদের মতে এই তত্ত্ব ‘বাইবেল বিরোধী’। এই শিক্ষক এবং ছাত্ররা জৈববিবর্তন তত্ত্ব পড়েনি বলেই হয়তো তারা নির্বিচারে এরকম একটি অবস্থান নিয়েছিল। অতএব, জৈববিবর্তন তত্ত্ব পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তা উপযুক্ত শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্রদের শেখানো খুব জরুরী।
জীববিজ্ঞানের যেসব প্রায়োগিক ক্ষেত্রে জৈববিবর্তনের জ্ঞান ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং প্রযুক্ত হবার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে সেটি হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞান। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে এদেশের চিকিৎসকদের শতকরা ৯৯ ভাগই সে কথা জানেন না। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক জার্নালের ২০০২-এ প্রকাশিত নিবন্ধে লেখা হয়েছে, “গত বিশ বছরে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক অগ্রগতি হচ্ছে, এ ব্যাপারে নতুন করে স্পষ্ট স্বীকৃতি, যেকোনো জীবতাত্ত্বিক প্রবণতাকে বোঝার ক্ষেত্রে দুই ধরনের ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়-
ক) একটি সন্নিহিত (Proximate) ব্যাখ্যা, অর্থাৎ প্রবণতাটি কিভাবে ক্রিয়া করে;
খ) একটি দূরবর্তী বা বিবর্তনিক ব্যাখ্যা, অর্থাৎ কী কারণে প্রবণতাটি অস্তিত্বশীল হয়েছে।
এরা একটি আরেকটির বিকল্প নয়; পুরিপূর্ণ বোধের জন্য এই দুটোই প্রয়োজনীয়।”
তবে ব্যতিক্রম হলেও আমাদের দেশেই মেডিক্যাল কলেজের এক শিক্ষক সুচিন্তা ও সাহসের সাথে কলেজের একটি একাডেমিক সেমিনারে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। এবং আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জৈববিবর্তনের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা। জৈববিবর্তন সম্পর্কে কৌতূহলী অনেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে জৈববিবর্তন সম্পর্কে জানতে চেয়ে হতাশ হন। অনেক সময় তাঁরা এমনও শুনতে পান, জৈববিবর্তনের সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই কিংবা এটি অপ্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার। এরকম সেমিনার আমাদের দেশে একটি বিরল ঘটনা এবং এটি হয়েছিল কারণ ব্যক্তিগতভাবে ওই শিক্ষক জৈববিবর্তনের চর্চা করতেন। তবু এটি আমাদের জন্য আশাজাগানিয়া একটি পদক্ষেপ। এ ধরনের সেমিনার, শিক্ষা কার্যক্রম এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় জৈববিবর্তনের প্রয়োগের যৌক্তিকতাকে তুলে ধরে। শুধু উচ্চ মাধ্যমিক নয় মাধ্যমিক পর্যায়েও যে জৈববিবর্তন পড়ানো প্রয়োজন, এ আলোচনা সে ব্যাপারটিকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে।
শেষ কথা
নানা সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে আমাদের দেশে জৈববিবর্তনের চর্চা অত্যন্ত অনগ্রসর পর্যায়ে রয়ে গেছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এটি যখন পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল তখনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে এবং উপযুক্ত শিক্ষকের মাধ্যমে বিষয়টি পড়ানো হয়নি। উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার ছাত্রদের অল্প একটি অংশ বিবর্তন ‘পেপার’টি নেন। কিন্তু তাঁদের শেখার এবং জানার পরিধি ও গভীরতা যে অগ্রসর কোনো পর্যায়ে যায় না তা তাঁদের পরবর্তী কার্যক্রম দেখলেই বোঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিশুদ্ধ বা ফলিত কোনো ক্ষেত্রেই এ বিষয় সম্পর্কিত কোনো গবেষণা হয়েছে কিংবা অন্য কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে জৈববিবর্তনের জ্ঞানের প্রয়োগ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর জীবতাত্ত্বিক মাত্রা বোঝার ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানের প্রয়োগ আমাদের দেশে খুব লক্ষণীয় নয়। বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে গবেষণা এবং প্রকৃতির সাথে সংস্রবের যে ঘাটতি রয়েছে জৈববিবর্তন চর্চার দৈন্যও এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে ছোটবেলা থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা জৈববিবর্তন পাঠের সুযোগ তৈরি করতে হবে। উচ্চতর পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষকদের পরিচালনায় পরিপূর্ণ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রায়োগিক ও গবেষণাক্ষেত্রেও এই বিজ্ঞানকে সংযুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও বই-পুস্তক, পত্রপত্রিকা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, বিকল্প ক্লাস ইত্যাদির মাধ্যমে এ বিষয়টির উপযুক্ত শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। প্রকৃত জ্ঞানের প্রসার ঘটলে বিরোধিতা, অজ্ঞতা এবং ভুল ধারণার অন্ধকার দূর হবে এবং আমাদের জাগতিক বোধের বিকাশের স্বার্থেই এদেশের জৈব বিবর্তন চর্চাকে আমরা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিয়ে যেতে পারব।
(মনিরুল ইসলাম লেখক, চিকিৎসক)