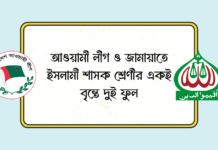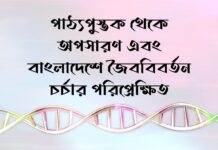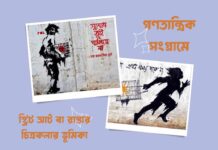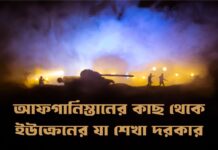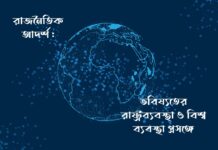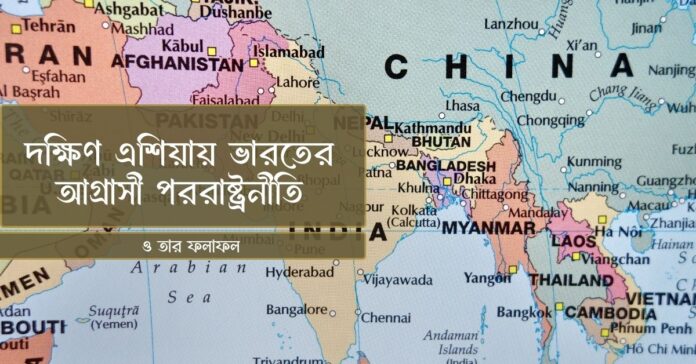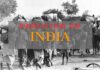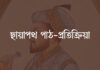গত ২০ জানুয়ারি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোঃ তৌহিদ হোসেন চীন সফরে যান। এটি ছিল তাঁর প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফর। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিগত ১৫ বছরে ফ্যাসিস্ট হাসিনার সময়ে বাংলাদেশের চারজন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সবাই তাঁদের প্রথম বিদেশ সফরের গন্তব্য হিসেবে ভারতকে বেছে নিয়েছিলেন।
এ ধরনের পরিবর্তন শুধু বাংলাদেশেই নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোতেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে. পি. শর্মা অলি ২০২৪ সালের ৩ ডিসেম্বর তাঁর প্রথম বিদেশ সফরে চার দিনের জন্য চীন যান। এর আগে নেপালের প্রধানমন্ত্রীরা সাধারণত প্রথম সফর হিসেবে ভারতকে বেছে নিতেন। একই ধারা দেখা যায় মালদ্বীপেও – বর্তমান প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু নির্বাচিত হওয়ার পর ভারত নয়, বরং চীনকে তার প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফরের গন্তব্য করেন। এটি মালদ্বীপের জন্যও একটি ব্যতিক্রম ঘটনা, কারণ এর আগে দেশটির সব প্রেসিডেন্ট প্রথম সফর করতেন ভারতে।
ভারতকে ঘিরে থাকা এই তিনটি প্রতিবেশী দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে এই পরিবর্তন স্পষ্টভাবে বর্তমান দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অবস্থান ও প্রভাব সম্পর্কে একটি নতুন ইঙ্গিত দেয়।
গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে গেলে বাংলাদেশে তাঁর সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। এর মধ্যদিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত তার আরেকটি অনুগত সরকারকে হারায়। কোটা আন্দোলন থেকে শুরু হওয়া জুলাই গণঅভ্যুত্থান এত দ্রুত ও শক্তিশালীভাবে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করবে – এটা ভারত সরকার কল্পনা করেনি। তারা মনে করেছিল, শেখ হাসিনা প্রশাসন, পুলিশ, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ওপর যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানো সম্ভব নয়। কিন্তু জনগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।
শেখ হাসিনার পতন ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং পররাষ্ট্র নীতির নীতিনির্ধারকদের ওপরও প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে বিজেপি ও আরএসএস নেতা রাম মাধব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। গত এক দশক ধরে ভারতের আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতির ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় দেশটি ক্রমশ বন্ধুহীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে – এ নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও বিজেপি, কংগ্রেসসহ বামপন্থী দলগুলো সবাই শেখ হাসিনার পক্ষে তাদের অবস্থান বজায় রেখেছে, তবুও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত যেভাবে একের পর এক অনুগত সরকার হারাচ্ছে – এমন পরিস্থিতি অতীতে দেখা যায়নি।
ভারতের শাসক শ্রেণী ও তাদের মূলধারার গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক নেতারা বাংলাদেশের এই পরিবর্তনকে আমেরিকা, পাকিস্তান ও চীনের ইন্ধন ও সহযোগিতার ফল বলে প্রচার করছে। মূলত, এটি তাদের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতা ঢাকার প্রচেষ্টা। তবে এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাকে খারিজ করে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এখন তারা আমেরিকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকে তাকিয়ে আছে, যাতে বাংলাদেশে আবার ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়।
কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের জনগণ কোনো বিদেশি শক্তির ইন্ধনে শেখ হাসিনার পতন ঘটায়নি। গত ১৫ বছর ধরে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে শেখ হাসিনা শত শত মানুষকে গুম করেছেন, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন। বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরেছেন এবং তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছেন। পরপর তিনটি ভুয়া নির্বাচন করে জনগণের সম্মতি ছাড়াই সরকার গঠন করেছেন। পাশাপাশি, লুটপাট, দমন-পীড়ন, এবং সাধারণ জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছেন।
এই দমননীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে প্রতিরোধের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কোটা আন্দোলনে সরকারি বাহিনীর দমন-পীড়ন সেই জমে থাকা ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করে, যা শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট শাসনের পতন ডেকে আনে।
শেখ হাসিনার এই চরম ফ্যাসিবাদী শাসনকে প্রত্যক্ষ সমর্থন দিয়েছে ভারত। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য চাপ দিলেও, ভারতের কূটনৈতিক চাপে তারা শেষ পর্যন্ত সেই অবস্থান থেকে সরে আসে। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনকে রক্ষা করতে ভারত পশ্চিমা বিশ্বকে বোঝায় যে এটি তাদের নিরাপত্তা স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারত-আমেরিকা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রকে জানায়, যদি বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়, তাহলে আওয়ামী লীগের বিরোধী দলগুলো জয়ী হবে এবং এর ফলে ইসলামপন্থী দলগুলোর শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ভারত এই যুক্তি দিয়েই পশ্চিমা বিশ্বকে শেখ হাসিনার স্বৈরতন্ত্র মেনে নিতে বাধ্য করে।
এর আগেও, ২০১৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছিল। সেই নির্বাচনে বিএনপি ও অন্যান্য বিরোধী দল অংশ না নিলে ভোটের বৈধতা নিয়ে সংকট দেখা দেয়। তখন ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশ সফরে এসে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরশাদ প্রথমে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলেও, ওই বৈঠকের পর হঠাৎ করেই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সুজাতা সিং বৈঠকে এরশাদকে স্পষ্টতই বলেন, তিনি যদি নির্বাচন না করেন, তাহলে জামায়াত-শিবিরসহ ইসলামী দলগুলোর উত্থান ঘটবে এবং তারা ক্ষমতায় আসতে পারে।
২০১৮ সালের রাতের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগকে জোরপূর্বক ক্ষমতায় রাখার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা ছিল সুস্পষ্ট। ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে সেই নির্বাচন ঘিরে সরাসরি তৎপর দেখা যায়। একের পর এক বিতর্কিত নির্বাচন ও ফ্যাসিবাদী দমননীতি টিকিয়ে রাখতে ভারত বারবার হাসিনা সরকারকে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সমর্থন দিয়েছে।
ভারতের হিন্দুত্ববাদী বিজেপির ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব ও আধিপত্যবাদী নীতি শুধু বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশকেও প্রভাবিত করেছে। সম্প্রতি মালদ্বীপ, নেপালসহ একাধিক দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি এই নীতিরই প্রতিফলন।
দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্য কমছে
২০২৩ সালের মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোহাম্মদ মুইজ্জুর ‘India Out’ স্লোগান দেশজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ধারণা করা হয়, তাঁর এই ভারতবিরোধী অবস্থানের কারণেই তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হন। নির্বাচিত হওয়ার পরপরই মুইজ্জু মালদ্বীপে অবস্থানরত ভারতের ১০০ সেনাসদস্যকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানান এবং শেষ পর্যন্ত ভারতকে তা মানতে বাধ্য করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মালদ্বীপের বিকল্প হিসেবে পর্যটকদের লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের আহ্বান জানান, যা দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংকট তৈরি করেছে।
নেপালের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্কের অবনতি দীর্ঘদিনের। ২০১৫ সালে নেপাল নতুন সংবিধান প্রণয়ন করলে ভারত তাদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। এর ফলে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছে যায়। ভারতীয় আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে নেপাল ২০১৬ সালে চীনের সঙ্গে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যদিও এর আগে ভারতই ছিল তাদের একমাত্র জ্বালানি সরবরাহকারী। ২০১৭ সালে নেপাল চীনের Belt and Road Initiative (BRI) প্রকল্পে যোগ দেয়, যা ভারতের জন্য ছিল এক বড় কূটনৈতিক ধাক্কা।
ভারতের শাসকগোষ্ঠীর অহংকারী ও আধিপত্যবাদী নীতির কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় তারা ক্রমেই বন্ধুহীন হয়ে পড়ছে। নেপাল, মালদ্বীপসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর জনগণের মধ্যে ভারতের প্রতি ক্ষোভ দীর্ঘদিনের, যা এখন প্রকাশ্যে আসছে।
বাংলাদেশে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বিজয়ে আমরা দেখেছি কিভাবে জনগণ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবন দখল করেছেন। মাত্র দুই বছর আগে শ্রীলঙ্কাতেও আমরা একই দৃশ্য দেখেছিলাম, যখন গণবিক্ষোভের মুখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষে পালিয়ে যান। তাঁর উত্তরসূরি, ভারতপন্থি রনিল বিক্রমাসিংহ, সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিশাল পরাজয় বরণ করেছেন। নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন জনতা বিমুক্তি পেরামুনা (জেভিপি) নেতা অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে, যিনি ঐতিহাসিকভাবেই ভারত বিরোধী অবস্থানে থেকেছেন। নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি ভারতের আদানি গ্রুপের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের প্রতিশ্রুতি দেন। নরেন্দ্র মোদী যখন নির্বাচনী জনসভায় দাবি করেন, ভারতের ন্যায্য অঞ্চল শ্রীলঙ্কাকে তার বিরোধী দলগুলো দিয়ে দিয়েছে, তখন শ্রীলঙ্কায় ভারতবিরোধী মনোভাব আরও তীব্র হয়।
ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ১৯৪৭ সালের পর থেকেই বৈরী। আফগানিস্তানে তালেবানরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও খারাপ হয়েছে। ২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর আফগানিস্তানের ভারতীয় দূতাবাস বন্ধ হয়ে যায়, কারণ তালেবান প্রশাসন পর্যাপ্ত কূটনৈতিক সহায়তা পায়নি।
ভারতের জন্য আরেকটি বড় কূটনৈতিক ধাক্কা অপেক্ষা করছে মিয়ানমারে। বর্তমানে দেশটি সামরিক জান্তার শাসনে থাকলেও সেখানে বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব বাড়ছে। কিন্তু ভারত জান্তা সরকারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, বিরোধী শক্তিগুলোর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশে যেমন ভারত তার সমস্ত কূটনৈতিক বিনিয়োগ আওয়ামী লীগে করেছিল, একই ভুল তারা আফগানিস্তান ও মিয়ানমারেও করেছে। জনগণের আকাক্সক্ষার দিকে না তাকিয়ে ভারত সবসময় কর্তৃত্ববাদী শাসকদের সমর্থন দিয়েছে, যার ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় তারা ক্রমেই বন্ধুহীন হয়ে পড়ছে।
দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের ‘Neighbourhood First’ নীতির ব্যর্থতা
২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত সব রাষ্ট্রপ্রধান বা তাদের দূত উপস্থিত ছিলেন। তখন ভারত ঘোষণা দেয় যে তাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হবে ‘Neighbourhood First’ বা ‘প্রতিবেশী প্রথম’ নীতি। তবে বাস্তবে এই নীতি যে একপ্রকার ফাঁকা বুলি ছিল, তা বর্তমান পরিস্থিতি দেখলেই বোঝা যায়। মুখে প্রতিবেশী প্রথম বললেও, ভারতের প্রকৃত নীতি ছিল India First – ‘ভারত প্রথম’, যার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার হয়নি, বরং দুর্বল হয়েছে।
এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)-এর নিষ্ক্রিয়তা। ২০১৬ সালে জম্মু-কাশ্মীরের উরিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর সন্ত্রাসী হামলার (যাতে ১৯ জন সেনা নিহত হয়) পর ভারত ইসলামাবাদে অনুষ্ঠেয় সার্ক সম্মেলন বর্জন করে। এরপর থেকেই সার্ক কার্যত অচল হয়ে যায়।
২০১৪ সালে নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যই ভারতের কৌশল স্পষ্ট করে— ‘The bonds will grow. Through SAARC or outside it. Among us all or some of us.’
অর্থাৎ, ভারত সার্ককে উপেক্ষা করে নিজেদের সুবিধামতো অঞ্চলভিত্তিক জোট গঠনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই নীতির ফলশ্রুতিতে তারা BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ও BBIN (Bangladesh-Bhutan-India-Nepal Initiative) এর দিকে মনোযোগ দেয়। তবে ভারতের নেতৃত্বে গঠিত এই সংস্থাগুলোও কার্যত কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।
এর ব্যর্থতার কারণ ভারতের নীতি। ভারত কখনোই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বহুপাক্ষিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে চায়নি, বরং সব দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে উৎসাহিত করেছে। বহুপাক্ষিক জোট গড়ে উঠলে ছোট দেশগুলোর কণ্ঠস্বর শক্তিশালী হতো, যা ভারত এড়াতে চেয়েছে। ভারত চেয়েছে প্রতিটি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাধ্যমে নিজেকে সুবিধাজনক অবস্থানে রাখতে, যাতে তারা স্বল্পমেয়াদে সুবিধা নিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা না থাকে।
এ কারণেই ভারতের Neighbourhood First (প্রতিবেশী প্রথম) নীতি বাস্তবে Neighbourhood Ignored (প্রতিবেশীকে উপেক্ষা) নীতিতে পরিণত হয়েছে।
দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতার কারণ
ভারতের দক্ষিণ এশিয়া নীতির ব্যর্থতার পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ রয়েছে, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীর উগ্র হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের উত্থান। এটি শুধু ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করেনি, বরং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গেও সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ইউরোপের মতো শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোটের অনুপস্থিতি পরস্পরের মধ্যে আস্থার অভাব সৃষ্টি করেছে। SAARC-এর মতো সংস্থাগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি, যার মূল কারণ ভারতের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ভারতের স্বার্থের বাইরে গেলে যে কোনো আঞ্চলিক উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে।
দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক উত্তেজনার অন্যতম প্রধান কারণ ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তৎকালীন ভারতীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। দেশভাগের সহিংসতা, কাশ্মীর ইস্যু ও দুই দেশের পারস্পরিক অবিশ্বাস আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কখনোই সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের ছায়াতলে চলে যায়, যার চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে ১৯৭২ সালের ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ও শান্তি চুক্তিতে। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের একটি পরোক্ষ আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সরকার এ সম্পর্কের ভারসাম্য আনতে চেষ্টা করলেও ভারত কখনোই বাংলাদেশকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন কূটনৈতিক সত্তা হিসেবে মেনে নিতে চায়নি।
বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের দায়িত্ব ছিল ছোট প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করা। কিন্তু ভারতের শাসক শ্রেণী বরাবরই অহংকারী ও আধিপত্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দিয়েছে।
১৯৯০-এর দশকে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে যে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেন তা Gujral Doctrine নামে পরিচিতি লাভ করে। এই নীতির মূলকথা ছিল—ভারত একটি বড় দেশ হিসেবে ছোট প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বিনিময়ের প্রত্যাশা ছাড়া সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলবে।
কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই নীতিকে কার্যত বাতিল করে দেয়। উগ্র জাতীয়তাবাদী কৌশলের কারণে ভারত প্রতিবেশীদের আস্থা অর্জনের পরিবর্তে শত্রুতার আবহ তৈরি করেছে।
২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ভারতের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি আরও বিস্তৃত হয়েছে। বিজেপির আদর্শিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (RSS) এর ‘অখণ্ড-ভারত’ ধারণা এবং মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করেছে। বিজেপি শুধু ভারতের মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধেই বিদ্বেষ ছড়ায়নি, বরং প্রতিবেশী দেশগুলোর মুসলমানদের বিরুদ্ধেও প্রোপাগান্ডা চালিয়ে এসেছে। বিশেষ করে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রচারণায় ব্যবহার করে বিজেপি নিজেদের হিন্দুত্ববাদী অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে।
লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশকে ‘অনুপ্রবেশকারীদের দেশ’ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গত বছর ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের কথা বললেও, ক্ষমতাসীন দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এই দাবিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি মহারাষ্ট্র ও দিল্লির নির্বাচনে বিজেপি একই ধরনের প্রচারণা চালিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খানের ওপর হামলার ঘটনায় এক বাংলাদেশি নাগরিককে দায়ী করে ভারতের মূলধারার মিডিয়া ব্যাপক প্রচারণা চালায়, যা পরবর্তীতে সম্পূর্ণ ভুয়া প্রমাণিত হয়।
বাংলাদেশকে ইসলামি জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে চিত্রিত করার জন্য ভারতের মিডিয়া দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছে। শেখ হাসিনার পতনের পর ভারতের মিডিয়া বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের অসংখ্য ভুয়া খবর প্রচার করেছে, যা বাস্তবে ঘটেনি। এই ধরনের প্রচারণার মাধ্যমে বিজেপি শুধু বাংলাদেশকে নয়, বরং পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করছে। ভারতের এই আগ্রাসী নীতি ও উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব শুধু প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গেই নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ায় বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক সহযোগিতার পথকেও সংকুচিত করেছে। বিজেপি যদি সত্যিই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়, তবে তাদের মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণা ও আধিপত্যবাদী পররাষ্ট্রনীতি থেকে সরে আসতে হবে।
বিজেপির মুসলিম বিদ্বেষী প্রোপাগান্ডার প্রতিক্রিয়া শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় সীমাবদ্ধ নেই, এটি মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও প্রভাব ফেলেছে। ২০০৬ সালে বিবিসির এক জরিপে ইরানের প্রায় ৭১% মানুষ ভারতকে তাদের বন্ধু হিসেবে মনে করলেও, বর্তমানে সেই সম্পর্ক অনেক খারাপ হয়েছে। ২০২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ভারতের মুসলমানদের অবস্থা ফিলিস্তিন ও মায়ানমারের নিপীড়িত মুসলমানদের সঙ্গে তুলনা করেন। একইভাবে, ২০২১ সালে কোভিড-১৯ মহামারির সময় ভারতের সাম্প্রদায়িক মিডিয়া যখন দিল্লির মসজিদগুলোকে ভাইরাস ছড়ানোর জন্য দায়ী করে, তখন ইন্দোনেশিয়া তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত ও ওমান থেকে মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য প্রচারের অভিযোগে কিছু ভারতীয়কে ফেরত পাঠানো হয়। কর্ণাটকে বিজেপি সরকার যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে, তখন কুয়েতের সংসদ সদস্যরা বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি তোলেন।
ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদী শাসনের উত্থান ও বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আধিপত্য তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে, নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গৌতম আদানির ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ শুধু ভারতেই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে আদানির বিদ্যুৎ চুক্তি ও শ্রীলঙ্কায় তার সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প এই আধিপত্যেরই অংশ। মোদী সরকার ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনার পক্ষে কাজ করেছে মূলত এই ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণেই। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্বনিম্ন, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সহযোগিতার অভাবকে চিহ্নিত করে। যেখানে ইউরোপে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ৫০%+ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ২৫%+, সেখানে দক্ষিণ এশিয়ায় এই হার মাত্র ৫%। ভারতের আধিপত্যবাদী ও সংখ্যালঘু-বিরোধী নীতির কারণে এই অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্য কমে যাওয়ার আরেকটি কারণ চীনের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক উপস্থিতি। চীন তার Belt and Road Initiative (BRI) কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি করছে এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাচ্ছে। ভারত যেখানে সার্ককে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে, সেখানে চীন নতুনভাবে China-South Asia Forum চালু করেছে, যা যদিও এখনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেনি, তবে এটি ভারতকে বাদ দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কাছে চীনকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি উদ্যোগ। বাস্তবতা হলো, ভারত যেভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, সেই জায়গায় চীন তার বিপুল বিনিয়োগ ও পরিকাঠামোগত সহায়তার মাধ্যমে তার প্রভাব বৃদ্ধি করেছে।
এটা স্পষ্ট যে, গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনার সরকার যেভাবে ভারতের স্বার্থে কাজ করেছেন, তাদের একের পর এক সুবিধা দিয়েছে, সেটা ভারত ভবিষ্যতে সহজে পাবে না। পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের সুবিধা, ফেনী নদীর পানি, আইটি খাতে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং আদানির কাছ থেকে ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ আমদানির মতো সুবিধা বাংলাদেশ বিনাশর্তে দিয়ে এসেছে। কিন্তু বিনিময়ে ভারত বাংলাদেশের স্বার্থের বিষয়ে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা নেয়নি। রোহিঙ্গা সংকটে ভারত নীরব থেকেছে, তিস্তাসহ ৫৪টি নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা দেয়নি, সুন্দরবনকে ঝুঁকিতে ফেলে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং সীমান্তে বিএসএফের মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা অব্যাহত রেখেছে।
নরেন্দ্র মোদী ভারতের আধিপত্যবাদী অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে চান, তবে বাস্তবতা হলো, তার কৌশল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে ভারতের থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। যদি ভারত গোয়েন্দা সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে, বরং জনগণের দৃষ্টিতে এই অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অবস্থান কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে, নতুবা ভারত ক্রমশই আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।