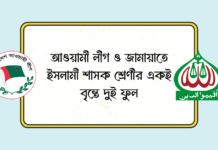বাংলার মানুষের ধর্ম চেতনা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রকৃতির সঙ্গেই তার নিবিড় সম্পর্ক। ঋতুর সাথে মিলিয়ে তারা যেমন ফসল উৎপাদন করে, জমি চাষ করে, তেমনি ধর্ম সাধনাও করে। এই ধর্মটা হচ্ছে মানবিক ধর্ম। এই মননধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্য সৃষ্টি করেছে, কোনোরকম বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। এর মধ্যে রয়েছে মরমীবাদ। সর্বজনীন লোকচর্চার মধ্যেই এই ভাববাদী ধারণার নির্যাস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এবং এর মধ্যে নানারূপ বৈচিত্র্য। মানুুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ ও বৈষম্য এই সমাজে নেই। বাঙালির চরিত্র গড়ে উঠেছে মানুষকে নিয়ে।
বাঙালায় সর্বধর্মের মানুষের সমাবেশ ঘটেছে : “The taste for toleration has deep roots, but it is not necessarily from one’s ancestors that one acquires it. The roots stretch back to ancient India. Which has the longest tradition of toleration in the world. There the major religions, and many others coexisted more or less harmoniously for over a thousand years. (An Intimate History of Humanity, Theodore Zeldin, Minerva, 1995, p 262)”
জেলদিন একজন সুপণ্ডিত। ফরাসি দেশের এই খ্যাতিমান গবেষক ভারতীয় লোকদর্শন নিয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা যথার্থ। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন: “Some Hindus worship Vishnu and some Siva, each looking upon their God as supreme, but each accepts that the others God is worthy of worship too, and that ultimately, perhaps both sides are right.
এর পরে তিনি বলেছেন: Hinduism started 5,000 years ago with the premise that things are more complex than they seem, that reason is not enough to discover the truth, and that one gets to the truth depends not just on one’s knowledge but on the sort of persons one is, how moral one lives.” (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৬২)
হিন্দু মানসিকতা সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিষ্ণু এবং শিব পূজা দর্শনগতভাবে আপাতত বিরোধী দর্শন কিন্তু এই দর্শন দ্বিবিধ হলেও পরস্পরে মনে গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় কোনো মনোভাব আছে বলে মনে হয় না। এ নিয়ে স্ববিরোধিতা থাকলেও হিন্দু বলে থাকেন: Contradiction of life have to be accepted, even through this can produce disconnecting results (প্রাগুক্ত পৃ. ২৬৩)। অর্থাৎ এটাই হলো এই দেশীয় লোকসমাজের আত্মদর্শন। সুদূরকাল থেকে চলে আসছে এই ভাব চেতনা। এটাকে বলা হয়ে থাকে লোকধর্ম। বেঁচে থাকাটাই হলো কৃষ্টি। জীবন সাধনা ও কর্ম সাধনা হলো অনন্ত পথ যাত্রার পাথেয়। এই লোকধর্মের বিশেষ কোনো প্রবর্তক নেই। অর্থাৎ অপৌরুষের ধর্ম। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এদেশে যারা এসে বসতি গেড়েছে, তাদের সংস্কৃতি তাদের ধর্মমত একত্রিত হয়ে এদেশের মানুষের স্বভাব ও চেতনার মধ্যে মিলে মিশে রয়েছে। যখন কোনো বৈষম্য ও অসঙ্গতি সমাজের মধ্যে মাথা তুলে দাড়িয়েছে, তখনই দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে ভাববিদ্রোহ।
স্বভাববাদী বাঙালি বর্ণবৈষম্যকে স্বীকার করেনি। ব্রাহ্মণতন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রকে অস্বীকার করেছে। মনুবাদী হিন্দু মতবাদ মানবতাবাদীরা জীবন ধর্মের মূল থেকে বিচ্ছেদ করে সত্যের স্বরূপ উন্মোচন করে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। সত্যের স্বরূপ সন্ধানী হলো বাঙলার ধর্মচেতনার উৎস। ধর্মের নামে কোনো বৈষম্য যখন সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তখনই দেখা দিয়েছে বাঙলার ভাবুকরা, ভাবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে যুুক্তিবাদী বাঙালিরা অসাম্যের বিরুদ্ধে এমনই একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, যা ইতিহাসে বৈষ্ণববাদী আন্দোলন হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। এই আন্দোলন ছিল বর্ণবাদ, হিংসা, বিদ্বেষ ও অসাম্যের বিরুদ্ধে একটি মানব কল্যাণকামী অহিংসা আন্দোলন। এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক অংশগ্রহণ করেছিল। (শ্রী চৈতন্যদেব ও তাহার পার্ষদগণ, শ্রী গিরিজা শঙ্কর চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ৫০)
হিন্দু সম্প্রদায় থেকে ‘শ্রী অদ্বৈত প্রচার করেছিলেন কী করে হিন্দুর সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দূর করা যায়, আর মুসলিম সম্প্রদায় থেকে হরিদাস প্রচার করেছিলেন কী করে মুসলমানদের সংকীর্ণতা দূর করা যায়। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০)
উল্লেখ্য, হরিদাস ছিলেন যবন, অর্থাৎ মুসলমান। তার জন্মস্থান সোনাই নদের তীরে, কেরলাগাছি গ্রামে। বর্তমানে গ্রামটি সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার অন্তর্গত। তিনি অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করে বেনাপোলের নিকটবর্তী পাটবাড়ির জঙ্গলে ভাবসাধনায় নিমগ্ন হন।
পরবর্তীকালে নবদ্বীপে গমন করেন এবং শ্রী চৈতন্যদেবের ভাববাদী আন্দোলনে শরিক হন। শ্রী রায় চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে, শ্রী চৈতন্য যবন হরিদাসকে বৈষ্ণব মতবাদে দীক্ষা দেননি বরং যবন হরিদাসই টোলের পণ্ডিত নিমাইকে টোল ছাড়িয়ে নতুন ধর্মমত প্রচারে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। হরিদাস চরিত্রের এটাই হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দিক।
‘ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালি যে নতুন ধর্মের আন্দোলন করিয়াছিল, প্রচার করিয়াছিল, গ্রহণ করিয়াছিল। ইতিহাস ইহার সাক্ষী।’ (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১) এই নতুন ধারা আন্দোলন ছিল হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত চিন্তা প্রসূত নব্যযুগের একটি ফলক। অনেকেই এই ঘটনাকে উভয় সম্প্রদায়ের যুক্ত সাধনা বলে অভিহিত করেছেন। এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের মহামিলন বলে অভিহিত করেছেন। এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের মহামিলন পৃথিবীর মানব ইতিহাসে বিরল। এই আন্দোলন ছিল শ্রেণী, বৈষম্য ও জাতপাতের বিরুদ্ধে। সকল রকম অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ বর্জন করে এই আন্দোলনের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। এ সম্পর্কে হোসেনুর রহমান মন্তব্য করেছেন : ‘মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে ভারতীয় ইসলাম কত স্বকীয়তা প্রধান, কতটা ভারতবর্ষ-প্রধান আজকের এই সঙ্কটকালে আমরা তা’ যেন বুঝতে চেষ্টা করি। ইসলাম চৈতন্যদেবকে যত প্রভাবিত করেছে, তিনিও ততটাই প্রভাবিত করেছেন ইসলামকে। চৈতন্যদেব ও যবন হরিদাস মধ্যযুগে বসেই নতুন এক কর্মের প্রয়োজনের কথা ভেবেছিলেন। এই ভাবনাকেই আজকের বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ‘Liberal pluralism of approach’ বলা হয়েছে। সেদিন নীলাচলে মহাপ্রভু বুঝেছিলেন এই পৃথিবীর মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো : The spiritual discovery of people of other faith’. আজ দ্বিতীয় পোপ পল এবং দালাই লামা এক বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার সামনে এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে ঘোষণা করেছেন। গান্ধীর ভাষায়: The searcher after truth should be humbler that the dust, This is the key to the discovery of others and to the peace keeping’। (হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা, হোসেনুর রহমান, ভারত বাংলাদেশ ২০০০, পৃ. ১৬)
প্রকৃতপক্ষেই বৈষ্ণব আন্দোলন ছিল একটি সামাজিক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছিল উভয় সম্প্রদায়ের জাতপাত, বৈষম্য ও নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের প্রতিবাদী বিদ্রোহ।
বাঙালায় সকল ধর্ম ও মতের লোক আবহমানকাল থেকে একত্রিত বসবাস করে এসেছে। কারোর সঙ্গে কারো কখনো বিরোধ দেখা দেয়নি। যার যার ধর্ম সেই সেই নিজের মতো করে পালন করে এসেছে। এখানে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে উচ্চ বর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্ণের মানুষের। যারা ধর্মপ্রচার করেছিলেন, তাদেরও আহ্বান ছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদাভেদ দূর কর, মরমী চেতনায় আলোকে মানুষকে উজ্জীবিত কর। সকলেই চেয়েছেন সার্বজনীন লোকচর্চার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক গড়ে তুলতে।
তাই বাংলার যে সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে, এই সংস্কৃতির উৎস হলো মনুষ্যত্ব সাধনের লোকসংস্কৃতি।
এই মানুষ বাংলার অধ্যাত্ম চেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। মনুষ্যত্ব সাধনই ছিল তাদের মূল দর্শন। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে এই সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ঘটেছে।
ষোলো শতকে নবদ্বীপে নবজাগরণের যে দীপশিখা জ্বলে উঠেছিল, এই শিখা নির্বাপনের পক্ষে শাক্ত শ্রেণীর কম প্রচেষ্টা ছিল না। নবদ্বীপের কোতওয়াল জগাই মাধাই বৈষ্ণববাদীদের উচ্ছেদ করার জন্য যে নিপীড়িনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তা ইতিহাসে আজও বিধৃৃত আছে।
বৈষ্ণব মতবাদের বিপক্ষে উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্ণের অভিজাত হিন্দু শাক্ত মতবাদকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকলেও উভয়ই পক্ষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এটা যে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান, তা নয়, সর্বধর্মের মধ্যে বিদ্যমান। হিন্দুধর্মের মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের লোক আছে, তেমনি মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় ও জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের সংঘ্যাত রয়েছে। বাঙালি মানসের চেতনার মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটছে। এই ঐতিহাসিক চেতনাকে কেউ কেউ বলেছেন – বাঙালি আত্মদর্শন। অর্থাৎ সকল মতবাদিরা মেনে নিয়েছেন- Contradictions of life have to be accepted ।
একথা সত্য যে, পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুধর্মের কোনো প্রবর্তকের আবির্ভাব হয়নি। যুগান্তরের যুগগুরু বা ঋষি মহাঋষিরা যা বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছে, সেটাই তারা গ্রহণ করেছে এবং মান্য করেছেন। ইহলোক নিয়ে সাধনা করেছেন পরলোক নিয়ে সাধনা করেছেন- প্রকারান্তে একটা ভাববাদী চেতনার উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়।
ভারতীয় উপমহাদেশে যতগুলো ধর্ম সম্প্রদায় আছে, সকল ধর্ম সম্প্রদায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিকে বিশ্বাসে আস্থাশীল। এদেশে এই ধর্মবিশ্বাসকে মধ্যমণি করে যে জীবনচর্যার বাস্তবায়ন ঘটেছে, সেটাই পরবর্তীকালে মানবমণ্ডলীর নানারকম কর্ম ও চিন্তায় সংস্কৃতিতে রূপান্তর হয়েছে।
আবার কখনো কখনো এক মতাদর্শের সঙ্গে অন্য মতাদর্শের সংঘাত ঘটেছে। ধর্মে গোড়ামি আশ্রয় করে যারা হেঁটেছেন, তাঁরাই তাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উন্মাদনা সৃষ্টি করে সমাজ অভ্যন্তরে হিংস্রতার জন্ম দিয়েছেন। সকল রকম ধর্মাশ্রয়ীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতা তখনো যেমন ছিল, এখনো তেমনি রয়েছে। উনিশ শতকে রামমোহন গোড়া হিন্দুপন্থীদের গোঁড়ামির মূলোচ্ছেদ করতে গিয়ে ব্রহ্মবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নতুন মতবাদ ও যুগোপযোগী ধারণা। গোড়াপন্থী হিন্দু সমাজ তাঁর এই নব্যভাবনার প্রতি কটাক্ষ করে জোটবদ্ধ হয়ে রামমোহনের অগ্রগমনের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু শাস্ত্র নিয়েও বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়েছিল।
পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম আছে – সবধর্মেই আছে অন্ধ আবেগপ্রবণতা। এই আবেগের মধ্যে মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। অন্ধ বিশ্বাসই হলো ধর্মের মূল শর্ত। যুক্তিতর্কের দ্বারা কোনো লোকের বিশ্বাসকে বিচ্যুত করা সম্ভব নয়।
প্রকৃতপক্ষে ধর্ম কোনো অলৌকিক বস্তু নয়। অথচ এই ধর্মবোধ মানুষের মনকে অন্ধ আবেগে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। এর থেকে বেরিয়ে আসার অর্থ হলো প্রচলিত বিশ্বাসে অস্বীকার করে পথচলা।
রামমোহন প্রচলিত ধর্মকে অস্বীকার না করে ধর্মের নামে যে কুসংস্কার ছিল সেই কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর সরিয়ে হিন্দুধর্মকে মনুষ্যধর্মে মর্যাদা দিয়েছিলেন। এর জন্য প্রাচীনপন্থীরা তার কর্মের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয়েছিল দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। পক্ষ বিপক্ষ দুটি সম্প্রদায়ে হিন্দু বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন টিকেছিল এই দ্বন্দ্ব। প্রাচীন সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সমস্যা সৃষ্টি হয় বিধবা বিবাহ নিয়ে। বিদ্যাসাগরের যুক্তির বিপক্ষে পাল্টা যুক্তি খাড়া করেও প্রাচীনপন্থীরা পরাজয় বরণ করেন।
খ্রিস্টধর্মেও রয়েছে দুটি বিবদমান দল – ক্যাথেলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। দুটি পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায় হিসাবে তারা পরিচিতি। দুটি পক্ষের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন। একদল অপরদলকে শত্রু হিসেবে বিবেচিত করে। ধর্মবাদীদের আধিপত্য বিস্তারিত হওয়ার ফলে ভূমিদাস প্রথা, জবদস্তিমূলক শ্রমদাসত্ব আরো বলবত হয়। চার্চ ধর্মের নামে মানুষকে শোষণ ও শাসন করে এক ভয়াবহ অবস্থার জন্ম দেয়।
ইউরোপে আঠারো শতকে খ্রিস্টধর্ম অর্থাৎ ক্যাথোলিক চার্চের প্রতি জনগণ বিদ্রোহ করে। অস্ট্রিয়ার সম্রাট চার্চের কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, চার্চের বিপুল সম্পদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। এমনকি অভিজাতদের আধিপত্য কঠোরভাবে দমন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যেমনি ছিল ঠিক তেমনি থেকে যায়।
ইউরোপে অভিজাত শ্রেণী ছিল চরম সুবিধাভোগী। অভিজাত ও যাজকরা ছিলেন সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। এই সুবিধাভোগীরা নিজেদের স্বার্থে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির রক্ষক ও খুঁটি হিসেবে সমাজ ব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত করে।
হিন্দুদের পূজাপার্বণে ব্রাহ্মণদের যেমন একচাটিয়া আধিপত্য রয়েছে। তেমনি খ্রিস্টান জগতে রয়েছে চার্চের যাজক সম্প্রদায়ের আধিপত্য। ব্রিটেনে প্রাক রেনেসাঁস আমলে রাষ্ট্র্রশক্তির প্রধান খুঁটি ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। রেনেসাঁসের ফলে জাতীয় চেতনা প্রধান হয়ে ওঠে। ধর্মের স্থান হয় দ্বিতীয় সারিতে।
বাঙলায় ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু হয়েছে কতকাল আগে থেকে এটা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেক গবেষক বলেছেন পাল আমল থেকেই এদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। এই ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল সাম্যবাদ। বাংলায় উঁচু-নিচু সমাজে বৈষম্য থাকায় নিগৃহীত, পদদলিত, লজ্জিত, অবহেলিত জনগণই এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যাঁরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন তাঁরা রাসুলের (দ.) একটি মহান বাণীকে প্রধান্য দিয়েছিলেন। সেই বাণীটি হলো : ‘সকল মানুষ সমান। ভালো বাসুক অথবা ঘৃণা করুক, সকল অবস্থাতে মানুষ মানুষের ভাই। যে পর্যন্ত কেউ ভাইয়ের জন্য তা না ভালোবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে।’ এই মর্মবাণী এদেশের নিপীড়িত-পদলিত মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। হিংসা-বিদ্বেষে আচ্ছন্ন বৈষম্যের সমাজে নিঃগৃহীত মানুষেরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়ে ওঠে।
এই বহুধাবিভক্ত সমাজে যে সামাজিক রীতি ব্যবস্থা ও প্রথা প্রচলিত ছিল, যে সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, তার ওপর কোনো ইসলাম ধর্ম প্রচারক হস্তক্ষেপ করেননি। এর ফলে একটা মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। যেমন ক্ষেতে ফসল বোনার সময় কৃষক একটা রীতি পালন করতো। তেমনি গোলায় ধান তোলার সময় সিঁদুর দিয়ে লক্ষ্মীর চিত্র গোলার দরজায় আঁকা হতো। লক্ষ্মীকে বলা হতো অন্নের দেবী। এটা দেশে কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরকম আরো কিছু প্রচলিত সংস্কৃতি ছিল। সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়।
তৎকালে বাংলাদেশের সর্বত্রই এর ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। পীর দরবেশদের নামে বিভিন্ন স্থানে দরগা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দরগায় উভয় সম্প্রদায়ের লোক বিপদ-আপদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে শিরনি মানত প্রদান করত। এটা নিয়ে কখনো সংঘাত সৃষ্টি হয়নি। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির একটা সমন্বিত রূপ এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান। পীরমাহাত্ম্য কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে প্রধানত পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম ঠাকুরের মধ্যে মুসলিম প্রভাব যথেষ্ট। এদেশের ভাবুক সমাজ ধর্ম ঠাকুরকে পীরের মর্যাদায় সম্মান জানিয়েছে। রূপরাম চক্রবর্তী নিজেকে রূপরাম ফকির বলে অভিহিত করেন। বাঙালি সমাজে পরবর্তীকালে এদেরকে অভিহিত করা হয়েছে ‘সত্যপীর’ ও ‘সত্যনারায়ণ’ হিসেবে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বহুস্থানে রয়েছে গাজী পীরের থান। সেই সকল থান ঘিরে নানারকম উৎসব হয়। নাথগুরু মৎস্যোন্দ্রনাথ ও পীর মসনদ আলিকে সমন্বিত করে ‘মছন্দলী’ বা ‘মছরা’ পীর হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে ক্যানিং রেলপথের ধারে ঘুটিয়ারী শরীফে গাজীর নামে একটি দরগাহ আছে। সেখানে আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় বড় রকমের একটা উৎসব হয়। হিন্দু ও মুসলমানরা মিলে এই উৎসব করে। এই এলাকাটি মেদন মল্ল পরগণার অন্তর্ভুক্ত। বারুইপুরের রায় চৌধুরীদের বাড়ি থেকে সর্বপ্রথম শিরনি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। হাঁড়োয়ায় আছে পীর গোরা চাঁদের দরগাহ। সেখানেও উভয় সম্প্রদায় তার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করে থাকে। খাড়ি গ্রামে আছে গাজীর দরগাহ। এছাড়াও রয়েছে গ্রামে গ্রামে বিবিমায়ের আস্তানা। রয়েছে পীর ফকিরদের সমাধি স্তূপ। এই স্তূপগুলো অনেকটা বৌদ্ধ স্তূপের মতো। এতে প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধ ধর্মীয়রা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করছে এবং তাদের সংস্কৃতিও বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।
দক্ষিণ বাংলায় রয়েছে বনবিবির প্রভাব। হিন্দু আমলে বনচণ্ডী নামে তাকে পূজা করা হতো। মুসলিম আমলে উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাকে বনবিবি নামে মানত দেয়। এই বনবিবির মূর্তির মাথায় রয়েছে টুপি। তার ওপরে আঁকা লতাপাতা। চুল বিনুনী করা। কপালে টিকলি। গলায় হার। তার পরিধানে মাখরা। পায়ে মোজা ও জুতা। হাতে আশাদন্ত। ফকিররা শিরনি হাজত দেন। কোনো মন্ত্রপাঠের রেওয়াজ নেই। বাংলার লৌকিক দেবতা গ্রন্থের লেখক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন যে, বনবিধি হলেন হিন্দুদেবী বনদুর্গা, বনচন্দ্রী, বনষষ্ঠী বা বিশালাক্ষী। মুসলমান আমলে বনবিবি নামে পরিচিত লাভ করেছেন; দুই ধর্মের বনদেবী হিসেবে স্বীকৃত। পাঠান রাজত্বকালে তিনি ছিলেন মুসলমান ধর্মসাধিকা ও ইসলাম প্রচারিকা। পরে দেবী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।
বাঙলা মঙ্গলকাব্যে এইভাবে তাকে বর্ণিত করা হয়েছে। বনবিবিকে নিয়ে পাঁচালি রচনা করেছেন মোহাম্মদ মুন্সী বয়নন্দী ও মুন্সী মোহাম্মদ খাতের সহ আরো অনেকেই। তাদের রচনায় বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদের কথা খুঁজে পাওয়া যায় না।
পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ড হারবার থানার কুলটিকরি গ্রামে প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার থেকে চৈত্র মাসের বারুনী স্নান পর্যন্ত বড়খাঁ গাজীসহ বিবিমার পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে বিবিমা প্রায় ২০০ বছরের অধিক প্রাচীন এবং জাগ্রত দেবী হিসেবে সর্বমান্য। পশ্চিমবঙ্গে পূজাপার্বণ ও মেলায় ৩য় খণ্ডে উল্লেখিত আছে, “প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার হইতে চৈত্র মাসের বারুনী তিথি পর্যন্ত প্রতি শান্তি মঙ্গলবার বিবিমা ও বড়খাঁ গাজীর বিশেষ হাজত পূজা ও উৎসব হইয়া থাকে এবং বারুনী তিথিতে পূজা ও পূণ্যস্নানের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ সহস্র নরনারী উৎসবে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত কীর্তনিয়ার দল প্রতি শনি ও মঙ্গলবার উৎসব প্রাঙ্গণে কীর্তন গান করিয়া থাকেন। আতপ চালসহ ফলমিষ্টির নৈবেদ্য এবং তুলশী পাতা ও বিশেষ করিয়া মোরগজটা ফুল দিয়া বিবিমার নিকট পূজা দেওয়া হয়। মানতস্বরূপ ভক্তরা কেহ কেহ ধূপ পোড়াইয়া থাকেন এবং কেউ একটি নির্দিষ্ট পুকুরে স্নান করিয়া দণ্ডী খাটেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বিবিমা ও বড়খাঁ গাজীর খাদেম রূপে পূজাদি করিয়া থাকেন। শোনা যায়, বহুকাল পূর্বে পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক হিন্দু বিবিমার সেবায়েত ছিলেন।
“ইহা ভিন্ন প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের যেকোনো একদিন ভক্তরা বিবিমার নিকট রুটি ও রান্না করা মুরগির মাংস দিয়ে পূজা দেন এবং এই দিনই গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা বিবিমার ঘরের আশপাশে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া উহা পরস্পরের সহিত বিনিময় করিয়া খাওয়া-দাওয়া করেন। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে ঝিলভাত পর্ব বলেন।”
এছাড়াও রয়েছে দক্ষিণ বাংলায় কালু গাজীর দরগাহ। কোথাও তিনি কালু দেওয়ান নামে পরিচিত। কালু গাজীর বেশ কিছু ভক্ত আজও আছে। হাসনাবাদ থানায় কালুতলায় তার নামে এক বিঘা জমির ওপর নজর গাহ ঢিবি রয়েছে। সেখানে একটি বাবলা গাছের তলায় ধূপবাতি জ্বালিয়ে তার ভক্তরা পৌষ সংক্রান্তিতে একদিনের উৎসব করে থাকে। অনেকেই কালু গাজীর মূর্তি তৈরি করে পূজা দেয়। এখানে হিন্দু-মুসলমানের বিপুল সমাগম ঘটে।
চারঘাটে ঠাকুরবর পীরের দরগাহ আছে। হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের লোক এই দরগাহে এসে শিরনি ও মানত দেয়। এই দরগাহ সম্পর্কে গিরিন্দ্র নাথ দাস উল্লেখ করেছেন, “ঠাকুরবর সাহেবের আস্তানাটি যেখানে অবস্থিত সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম, সেখানকার যে স্থানে তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল তার ওপরে নির্মিত দুটি দরগাহ গৃহটিও তেমন সুন্দর। একটা গম্বুজসহ চারকোণে ছিল চারটে মিনারেট। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে দুটি দরজা। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা ধূপধূনা বাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে। এখানে একদা মেলা বসত।”
তৎকালে গ্রামবাংলায় ওলাওঠা রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। লোকেরাই এই ওলা ওঠার প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ওলাওঠা দেবীর পূজা করত। ওলাওঠা ছিল লৌকিক দেবী। গ্রামবাংলার বহুস্থানে দেবীর থান আছে। পণ্যকুটিরে অথবা থানে ছয় বোনকে নিয়ে থাকতেন ওলাবিবি। তারা সাত বিবি নামে পরিচিত।
হিন্দু এলাকায় সাতবোনের নাম- রক্কিনী, সনকিনী, চমকিনী, রাওলি, বিলাসিনী, চণ্ডী, জামমালা, কাজিজাম।
মুসলমান এলাকায় সাতবোনের নাম- আসানবিবি, ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, আজগৈ বিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি, ঝেটুনে বিবি।
হিন্দুবর্ধিষ্ণু এলাকায় সাতবোনের চেহারা লক্ষ্মী, সরস্বতীর মতো এবং মুসলিম বর্ধিষ্ণু এলাকায় এদের চেহারা মুসলমান মেয়েদের মতো।
প্রতিবছর শীতকাল থেকে ফাল্গুন চৈত্র মাসে ওলাওঠা রোগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। কোনোরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। এই সর্বনাশা মড়কে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। মানব বসতিগুলো পরবর্তীকালে বনেজঙ্গলে পরিণত হতো।
হিন্দুরা এই দেবীর কৃপালাভের জন্য পূজাঅর্চনা করত। এবং মুসলমানরা সাতদিন সাতরাত্রি গ্রাম প্রদক্ষিণ করত এবং দুধকলা, আতপচাল, ও বাতাসা চটকে শরবত বানিয়ে গ্রামের লোকদের খাওয়াতো।
এ প্রসঙ্গে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মন্তব্য করেছেন, “পল্লী অঞ্চলে অনুন্নত শ্রেণীপূজিত সাতটি দেবী ভগ্নি, শাস্ত্রীয় সপ্তমাতৃকা থেকে এসেছেন। তাদের ঐ মন্তব্যের সমর্থনে বলা যায়- বাঙলাদেশের যে রাঢ় অঞ্চলে এই সাতটি লৌকিক দেবীদের পূজা প্রচলিত আছে সেই অঞ্চলেই এককালে সপ্তমাতৃকা পূজার প্রাধান্য ছিল জানা যায়। এই সপ্ত মাতৃকাদের দলীয় ইন্দ্রানী, বারাহী প্রভৃতির মূর্তি আজও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সেখানে দেখা যায়। মনে হয়, পল্লীর অনুন্নত সমাজ যখন শাস্ত্রীয় দেবতা পূজার বঞ্চিত ছিল, সে সময়ে সপ্তমাতৃকার অনুকরণে তাদের কল্পনা অনুযায়ী তারা এই ‘সাত দেবী ভগ্নির সৃষ্টি করেছিল, সেই দেবীরা কালক্রমে কোনো স্থানে ‘সাতবোন’ অন্যত্র ‘সাততন্ত্রী’ হয়েছেন, আবার মুসলমান যুগে দু’এক ক্ষেত্রে ‘সাতবিবি’তে পরিণত হয়েছেন। (বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, পৃ. ৯৮)
এই প্রকারের আপদ-বিপদের কালে লৌকিক সমাজ ব্যবস্থায় উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ জনশ্রেণীর মধ্যে ধর্মীয় কোনো নীতি ছিল না। সামাজিক ব্যবস্থার প্রচলিত বিষয়েই তারা আনুষ্ঠানিকতা পালন করত। মৌলিক দেবতার আরাধনা পদ্ধতিতে কোনো আড়ম্বর নেই। তাই হিন্দু-মুসলমানের আরাধনা ছিল একই পর্যায়ের। এটা ছিল ভক্তি পূজার এক বিরল দৃষ্টান্ত। মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটেছে বহু আগেই। এই মূর্তি সৃষ্টি আর্য সংস্কৃতির অবদান। এই প্রাচীন ব্যবস্থা বাংলার লোক সমাজের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান।
(হোসেনউদ্দীন হোসেন কথাসাহিত্যিক, গবেষক)