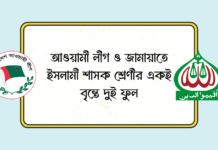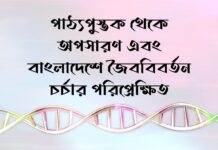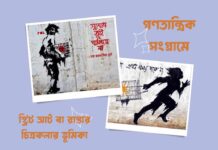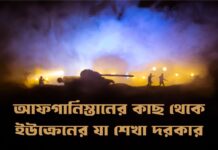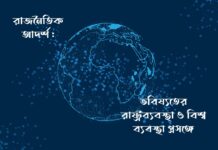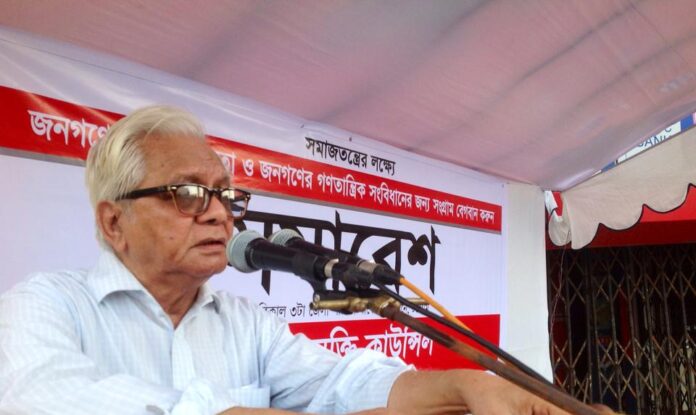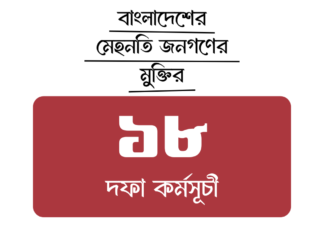বন্ধুগণ, ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এই এক বছরে কি হলো তার একটা হিসাব অবশ্যই দরকার। ২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে কথাটা এখন সামনে আসে সেটা হল এই অভ্যুত্থানের পর এদেশে কি ঘটলো কি পরিবর্তন হলো? দেখা যাবে অনেকেই মনে করেছিল যে এইটা একটা যাকে বলে দ্বিতীয় স্বাধীনতা, একটা বিরাট বিপ্লব ইত্যাদি। কিন্তু আসলে দেখা গেল এই যে পরিবর্তন এইটাতো কোন সমাজ বিপ্লব নয়। এই পরিবর্তন তো কোন শ্রেণী শাসনের পরিবর্তন আনেনি, এই পরিবর্তন তো এই দেশে যে শ্রেণী শাসন কাঠামো ছিল তাকে তো দুর্বল করেনি।
অভ্যুত্থানের পর দেখা গেল সামগ্রিকভাবে এই দেশের রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব। দক্ষিণপন্থী রাজনীতি দেখা যাচ্ছে অভ্যুত্থানের পর গত এক বছরে এখানে প্রবল প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এটা একটা লক্ষ্য করার মতো বিষয়। এই যে পরিবর্তন হলো এই পরিবর্তনটা তাহলে কি ধরনের পরিবর্তন? এই যে গণঅভ্যুত্থান গত বছর হয়েছিল জুলাই মাসে এর চেয়ে বড় গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের এই অঞ্চলে আর হয়নি। এত গভীর দেশ পর্যন্ত মানুষ আলোড়িত হয়েছে যার ফলে এই অভ্যুত্থান হয়েছে।
আর এই এত শক্তিশালী গণঅভ্যুত্থানের আরেকটা কারণ হচ্ছে এই অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে সব থেকে নির্যাতক, সবথেকে গণবিরোধী একটা শক্তির বিরুদ্ধে হয়েছে। এই গণঅভ্যুত্থানের পর যেটা অনেকেই সাধারণভাবে আশা করেছিলেন যে বামপন্থী শক্তি সামনে আসবে, কিন্তু দেখা গেল যে বাস্তব ক্ষেত্রে বামপন্থী শক্তি সামনে আসেনি। শুধু তাই নয় বলতে গেলে দেখা যাবে যে বামপন্থী শক্তি আশেপাশেও নাই। বামপন্থী বলে যে দলগুলো আছে তাদের কোন ভূমিকা এখানে নাই। কাজেই দক্ষিণপন্থী একটা প্রভাব এই রাজনীতিতে চলছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে যে ধর্মীয় প্রভাব এই ধর্মীয় প্রভাবটাও এখানে বেড়েছে। এদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব কমে এসেছিল সেটা কিন্তু এখন আর নাই। দেখা যাচ্ছে যে এখানে জামাতে ইসলামী যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে।
এইখানে ছাত্রদের যে দল হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির ক্ষেত্রেও দেখা যাবে এই জাতীয় নাগরিক পার্টিও ধর্মের কথা বলছে। এদের নেতৃত্বে একটা অভ্যুত্থান হয়েছে কিন্তু এখানেও চিন্তা করতে হবে, এদের নেতৃত্ব বলতে আসলে কি বোঝায়। এই যে বিশাল গণঅভ্যুত্থান হয়েছে এর নেতৃত্ব কি তারা দিয়েছে? ঘটনাক্রমে যেহেতু তারা কোটা আন্দোলন করেছিল এই কোটা আন্দোলন একটি স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করেছিল। শেখ হাসিনার যে নির্মম, নির্দয় এবং শক্তিশালী যে অবস্থান তার বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ হয়েছিল, এই ছাত্ররা করেছিল। ছাত্ররা কি নিয়ে আন্দোলন করছিল তারা তো সমাজের কোন বড় সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেনি। শ্রমিকের কথা, কৃষকের কথা তার মধ্যে ছিল না। এমনকি এদেশে গণতান্ত্রিক যে রাজনীতি সেই রাজনীতির কোন কথাও তাদের মধ্যে ছিল না। তাদের কথা ছিল যে তারা একটা সুবিধা ভোগী শ্রেণী হিসেবে তাদের নিজেদের মধ্যে কে কত কোটা পাবে তাই নিয়ে আন্দোলন।
তাহলে দেখতে হবে যে যেই ছাত্ররা এই আন্দোলনের তথাকথিত নেতা হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে তাদের আন্দোলনের চরিত্র কি ছিল, তার মধ্যে তো কোন রাজনীতি ছিল না। তার মধ্যে গরিবের কোন কথা ছিল না, কৃষক-শ্রমিকের কোন কথা ছিল না। তাদের কথা ছিল তাদের মধ্যে যে সুবিধা সেই সুবিধা কিভাবে পুনর্বণ্টন হবে সেই আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে সরকারের সাথে তাদের একটা সংঘর্ষ পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং এই সংঘর্ষের পরিস্থিতি বাংলাদেশের জনগণের যে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ ছাত্রদের এই বিক্ষোভ, ছাত্রদের এই দাবি তার সাথে যুক্ত হয়ে একটা বিশাল আন্দোলনের আকার, অভ্যুত্থানের আকার গ্রহণ করেছে। তাহলে এই এখানে এই আন্দোলন হয়েছে কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে দেখা যাবে কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নেই সমাজ পরিবর্তনের কোন চিন্তা ভাবনা নেই। এখানে জনগণের যে বছরের পর বছর সরকারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধের শক্তি সেই শক্তিরই একটা বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি।
এর ফলে যেটা হচ্ছে এই যে ছাত্রদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন হয়েছে এই আন্দোলনটা একটা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, খুব একটা চিন্তা প্রসূত আন্দোলন এরকম কিছু না। গণঅভ্যুত্থান যেটা বলা হচ্ছে এটা আসলে একটা বিস্ফোরণের মত ব্যাপার। গণঅভ্যুত্থান দু’রকম হতে পারে একটা হচ্ছে দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শীর্ষে একটা অভ্যুত্থান হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে কোন আন্দোলন করতে না পেরে দীর্ঘদিনের একটা আন্দোলনের প্রতিরোধের চেষ্টা সেটা ধামাচাপা থাকার ফলে একটা এমন পরিস্থিতি যেখানে সরকার ফেলে দেয়ার মত অবস্থা দাঁড়ায়। সেটা একটা আলাদা ধরনের অভ্যুত্থান।
বাংলাদেশে এই দ্বিতীয় ধরনের অভ্যুত্থান হয়েছে। এই যে অভ্যুত্থান হয়েছে এইটা কোন গণতান্ত্রিক কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলনের মাধ্যমে তার শীর্ষে এটা হয়নি। এটা হয়েছে একটা ব্যবস্থাকে হঠাৎ করে ভেঙে চুরমার করে দেয়ার মত পরিস্থিতিতে। কেননা এই পরিস্থিতির পর যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে এদেশের যেমস্ত সমস্ত শক্তি সামনে এসেছে। এই সমস্ত শক্তিকে কিন্তু প্রগতিশীল বলা চলবে না। দেখা যাবে যে প্রথম থেকে এদের মধ্যে শ্রমিকের কোন কথা নেই, কৃষকের কোন কথা নেই, কোন শ্রমজীবী মানুষের কোন কথা নেই। এবং তারপর দেখা যাবে যে তার কারণ হচ্ছে এই আন্দোলন তো কোন শ্রেণী কাঠামোর বিরুদ্ধে আন্দোলন না। কোন শ্রেণী পরিবর্তনের আন্দোলন নয়।
যে শ্রেণী এই দেশ শাসন করে এসেছে, এইযে ব্যবসায়ী শ্রেণী, ৭২ সাল থেকে বিকশিত হতে হতে হাসিনার আমলে একটা পর্যায়ে এসেছে তারাই শাসন করেছে তারাই আছে এখনো। হাসিনা পালিয়েছে কিন্তু এই দেশের যে শাসক শ্রেণী এটার তো কোন পরিবর্তন হয়নি। এই অভ্যুত্থান তো কোনো সামাজিক বিপ্লব না। একটা শাসক শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই এটা হয়েছে। তাহলে এই অবস্থার ফলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক দলগুলো এখানে এসেছে তাদের কারো মুখে শ্রমিক কৃষকের কথা শোনা যাবে না। বিএনপি একটা সংগঠন। এটা একটা এক ধরনের হাস্যকর ব্যাপারও বলা যেতে পারে, দুঃখজনকও বটে বাংলাদেশে এখন যে পরিস্থিতি হয়েছে তাতে এখন বিএনপিকেই মনে হচ্ছে সব থেকে প্রগতিশীল। কারণ তারাই কিছু কথাবার্তা বলছে। এইযে ছাত্রদের যে নতুন দল হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি এটা কি হলো?
ছাত্ররা নাকি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে ছাত্ররা আবির্ভূত হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু এদের তো কোন চিন্তা ভাবনা নেই, এরা তো কোটা নিয়ে আন্দোলন করেছে। এদের তো রাজনৈতিক অরিয়েন্টেশন বলে কিছু নাই। কোন প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা নাই। তাই প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছে তাদের যে বক্তব্য এখানে শ্রমিক কৃষকের কোন বক্তব্য নাই। শ্রমিক কৃষকের স্বার্থের কোন শব্দ তাদের নাই। তাদের একটা রাজনৈতিক দলের সংঘটিত হয়ে আরম্ভ করলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ইফতার পার্টি, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে লাখ লাখ টাকা খরচ করে ইফতার পার্টি। তার মানে ধর্মকে এরাও আকড়ে ধরল। তারা মনে করছে ধর্মকে ব্যবহার করা দরকার। এজন্য দেখা যাবে জামায়াতে ইসলামীর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি দেখা গেল।
এটার সাথে সাথে এইযে সরকার গঠিত হলো। সরকার একটা গঠিত হওয়া দরকার ছিল কারণ হাসিনাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর যে শূন্যতা শাসন ক্ষেত্রে তৈরি হল, সেটা তো একটা সরকার না হলে তো নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হতো সেটা রোধ হয়েছে এই সরকারের ফলে। কিন্তু বুঝতে হবে সরকারটাও যে এই শাসক শ্রেণীর তারই একটা দল। এই শাসক শ্রেণীর বাইরে তো না। এবং এই শাসক শ্রেণী দেখা যাবে পুরোপুরি এখানে সারভাইভ করার ফলে এই সরকারও এই শাসক শ্রেণীর একজন খেদমতগার হিসেবে থাকায় এখানে এক বছরে এমন কিছু ঘটেনি যেটাকে বলা যেতে পারে একটা আশা করার মত ব্যাপার।
এইযে গার্মেন্টস শ্রমিকরা রাস্তায় নামলে হাসিনার আমলে যেরকম লাঠি পেটা করা হতো পুলিশ দিয়ে এখনো সেইরকমই হচ্ছে এই সরকার লাঠি পেটা করছে। কাজেই এখানে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এই পরিস্থিতিটা গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আপাত দৃষ্টিতে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু যদি শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টাকে দেখা যায় তাহলে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। কারণ এই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কোন শ্রেণীগত কোন পরিবর্তন কিছুই হয়নি।
এই ছাত্ররা যে এসেছে এরা যে একটা রাজনৈতিক দল করেছে সেটা দেখা যাবে এটা শ্রেণীগত ভাবে তাঁরা মধ্যশ্রেণী সোজা কথায় বলতে এদেশের শাসক শ্রেণী, শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের মুখে শ্রমিকের একটা কথা কৃষকের একটা কথা বা দাবি দাওয়া কিছু নাই। লক্ষ্য করার মত বিষয় কি সমস্ত ইস্যু নিয়ে এখনকার রাজনীতি হচ্ছে। এখানে বারবার বলছি শ্রমিকের কোন কথা কৃষকের কোন কথা নাই। কাজেই এই অবস্থায় একটা সরকার আছে। এই সরকার এখনো পর্যন্ত হাসিনা যেরকম মার দিয়েছিল সেরকম মার দিচ্ছে না সেটার দরকারও হচ্ছে না। কিন্তু এই সরকার জনগণের স্বার্থে অনেক কতগুলো কমিশন করেছে। তারা সংস্কার করতে চাইছে এবং সংস্কার সংস্কার করে সবাই চিৎকার করছে। সংস্কার কিসের, সংস্কার তারাই চাইতে পারে যারা একটা ব্যবস্থাকে মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছে। স্বীকার করার পরে তার কিছু রদবদল করতে চাইছে।
যারা সংস্কার চায় তাঁরা তো উচ্ছেদ চায় না। আসলে দরকার যেই ব্যবস্থা এখানে রয়েছে তাঁকে উচ্ছেদ করা, যেই শ্রেণীর শাসন এখানে রয়েছে তাকে উচ্ছেদ করা। কিন্তু দেখা যাবে এই শ্রেণীর শাসন এখানে তেমনি রয়ে গেছে। এই শ্রেণীর শাসনে নির্যাতন অনেকটা লাগব হয়েছে কারণ নির্যাতনের অত দরকার হয়নি এই শাসন চালিয়ে যাওয়ার জন্য।
কিন্তু যে পরিস্থিতি আজকে রয়েছে সেই পরিস্থিতি চললে এইদেশে কোন উন্নতি হবেনা। এখন একটা নির্বাচনের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে কিন্তু এই নির্বাচন দিয়ে কি হবে। নির্বাচন করে এই শাসন কাঠামোর মধ্যেই একটা একটা দল আসবে। কাজেই এখানে এইযে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে মানুষের মনে যে একটা আশা সঞ্চার হয়েছিল, সেই আশা অনুযায়ী কোন পরিবর্তন তো হবেনা। সেই পরিবর্তন করতে হলে এই দেশে আন্দোলন করতে হবে। এইখানে যেটা বলা হয় সামনে একটা গণঅভ্যুত্থান করতে হবে, বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি। এটা তো এমনি হবেনা।
সাধারণ অভ্যুত্থান বা আমাদের দেশে যেটা হয়েছে এটাকে বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান কিছু বলা যাবেনা। যে বিপ্লবী গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজের মৌলিক কোন পরিবর্তন হবে। তার জন্য দরকার দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন পার্টির নেতৃত্বে, দলের নেতৃত্বে। সেরকম কোন প্রক্রিয়া এখনো এখানে দেখা যাচ্ছে না। যেটা বললাম এই অভ্যুত্থানের পর আশা করা গিয়েছিল যে এখানে প্রগতিশীল শক্তি, বামপন্থী শক্তি সামনে আসবে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল বাংলাদেশে এত বড় তুলনাহীন একটা গণঅভ্যুত্থানের পর দক্ষিনপন্থিদের রাজত্ব।
বামপন্থী বলে যে দল গুলো আছে তাদের তেমন সক্রিয়তাই নাই। এই অবস্থা কেন হলো এটাও একটা বিচার বিবেচনা করার প্রশ্ন। এইদেশে এই অবস্থা কেন দাঁড়ালো? এতদিনের একটা আন্দোলন সংগ্রামের পর এত বড় অভ্যুত্থানের পর প্রগতিশীল বামপন্থীরা সামনে এসে সব প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিনপন্থিরা সামনে এলো কেন। জামায়াতে ইসলামি এখন আগের যেকোনো সময়ের থেকে শক্তিশালী। ছাত্রদের যে নতুন দল হয়েছে সে দল টাও ধর্মের খুঁটিতে বাধা আছে। তাঁরা ধর্ম বিযুক্ত না। কাজেই কথা হচ্ছে এই যে দক্ষিনপন্থি ধর্ম কেন্দ্রিক যে রাজনীতি এটার প্রভাব এখানে রয়েছে। এর পাল্টা করতে গেলে যে আন্দোলন করতে হবে সেই আন্দোলনকারীদের কে শ্রমিকের কাছে, কৃষকের কাছে যেতে হবে। তারাই এদেশের আসল গণতান্ত্রিক শক্তি।
কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান সময়ে যে রাজনীতি হচ্ছে সেই রাজনীতির লোকেরা কেউ শ্রমিকের কাছে, কৃষকের কাছে যাচ্ছে না। লক্ষ্য করার মত বিষয় সেরকম সভা সমাবেশ ও তাঁরা করছে না কোন জায়গায়। এই যে একটা অবস্থা এর ফলেই কিন্তু দক্ষিনপন্থিরা, প্রতিক্রিয়াশীলরা এদেশে দাড়িয়ে আছে। এইখানে যে একটা সংগ্রাম করতে হবে এই সংগ্রামের মধ্যে দরকার সংগঠন। সংগঠন যেখানে নেই সেখানে তো কোনরকম সত্যিকার কোন আন্দোলন সম্ভব না। লেনিন বলেছিলেন জনগণের সংগঠন ছাড়া আর কিছুই নাই। সংগঠনই আছে জনগণের। সংগঠন না থাকলে কোন কিছুই হবেনা। যদি মনে করা যায় এইদেশে পরিবর্তন আনবো। পরিবর্তন তো বসে বসে হবেনা, পরিবর্তনের জন্য লড়াই করতে হবে। এবং লড়াই টা কি? লড়াই টার মানে হচ্ছে যারা ক্ষমতায় রয়েছে যারা দেশ শাসন করছে যারা জনগণের উপর শ্রমিক কৃষকের মাথার উপরের বসে আছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই তার মানে একটা মহাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই।
এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে তো সংগঠন থাকতে হবে। শক্তিকে পরাজিত করতে গেলে আমরা যে শক্তি নিয়ে দাঁড়াবো সেটা তাদের চেয়েও আরও বেশি শক্তিশালী হতে হবে। কিন্তু এই সংগঠন করার চিন্তা আমরা কিভাবে করছি। সংগঠন করার জন্য যেভাবে শ্রমিকের কাছে, কৃষকের কাছে যাওয়া দরকার আমরা কি যাচ্ছি? কাজেই আমরা যে কথা গুলো বলছি আসল কথা হচ্ছে নিজেদের সমালোচনা করা দরকার। আমরা অনেক কথা বলছি কিন্তু আমাদের সেই অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। মানুষের কাছে যেতে হবে খেটে খাওয়া মানুষের কাছে যেতে হবে তবেই না সংগঠন হবে। মধ্য শ্রেণীর কিছু লোক নিয়ে যে সংগঠন হবে সেই সংগঠন তার দ্বারা তো কোন সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব না। সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব একেবারে যারা খেটে খাওয়া লোক শ্রমিক, কৃষক, গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকের মধ্যে কাজ করা।
লেনিন যেমন বলেছেন সংগঠন দরকার। আমাদের যে সংগ্রাম এই সংগ্রাম করতে হলে সংগঠন দরকার। কাজেই আমাদের যে চেষ্টা সেই চেষ্টা প্রথমে সংগঠন করার জন্য করতে হবে। এছাড়া এগোনোর কোন উপায় নাই। কতগুলো ফাঁকা কথা বলে কোন কাজ হবে না। কারণ একটা শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে শক্তি অর্জন করতে হবে এবং এই শক্তি আসতে হবে কোত্থেকে লেনিন যেমন বলেছেন জনগণের সংগঠন ছাড়া আর কিছুই নেই জনগণকে লড়তে হলে তাঁকে সংগঠন করতে হবে। এই সংগঠন নিয়েই লড়তে হবে। লাঠি, গুলি, বন্দুক, জেল জুলুম সবকিছুর বিরুদ্ধে সংগঠন নিয়ে দাঁড়াতে হবে।
এই সংগঠন দিয়েই মার দিতে হবে, সংগঠন দিয়েই পরাজিত করতে হবে। আমরা শুধু কতগুলো কর্তব্য নির্দেশ করলেই হবে না। কতগুলো লক্ষ্য সম্পর্কে abstract way তে কথা বার্তা বললেই হবে না। বাস্তব কাজ করতে হবে শ্রমিকের কাছে যেতে হবে, কৃষকের কাছে যেতে হবে। এইযে শ্রমজীবী মানুষ তাদের মধ্যে যেতে হবে এবং কাজ করতে হবে। লেনিন বলেছেন যে প্রত্যেক দিনই তিনি রাত্রে হিসাব করতেন যে আজকে কি কাজ করলাম। একটা শ্রমিকের সাথে কি দেখা করলাম একটা সাংগঠনিক কোন ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিলাম। একটা চিঠি লিখলাম কি করলাম সন্ধ্যাবেলা বসে সেই খবর নিতে হবে।
আমরা যদি নিজের প্রতিদিনের খবর নেই তাহলে কি হবে তাহলে দেখা যাবে যে কিছুই নাই। এখন শ্রম ছাড়া তো কিছু হয় না। শ্রমই মানুষকে বড় করেছে। শ্রম বলে যে জিনিসটা সেটা তো জন্তু জানোয়ার করতে পারে না। কাজেই এই সংগঠন গড়ার জন্য শ্রম দিতে হবে, সময় দিতে হবে, নিজের অনেক কিছু ছাড়তে হবে। কাজেই এই অবস্থায় আমাদের সংগঠন করতে হবে। সংগঠনের খালি কর্তব্য নির্দেশ করলে হবে না, লক্ষ্য নির্দিষ্ট করলে হবে না, সেদিকে যাওয়ার পথে যেই শক্তি দরকার সেই শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং সংগঠন ছাড়া সেই শক্তি অর্জন করার অন্য কোন উপায় আমাদের পক্ষে গরিবের পক্ষে সম্ভব হবে না।
একটা লক্ষ্য যেমন নির্দেশ করতে হবে তেমনি আওয়াজ তুলতে হবে সংগঠন করার। মানুষের কাছে যেতে হবে, কৃষকের কাছে যেতে হবে, শ্রমিকের কাছে যেতে হবে। এই ঢাকা শহরে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রয়েছে। গার্মেন্টস শ্রমিক, অন্য শ্রমিকরা, সারা দেশে ছড়িয়ে আছে শ্রমিক। সবচেয়ে নির্যাতিত চা শ্রমিকেরা রয়েছে কিন্তু এই শ্রমিকের মধ্যে কোন কাজ নেই। যারা বামপন্থী সংগঠন বলে পরিচিত তাদেরও কোন কাজ নেই। তারাও হচ্ছে একটা মধ্যশ্রেনীর সংগঠন সেজন্য আজ তাদের পক্ষেও আর সামনে আসা সম্ভব না। কাজেই আমাদের সাংগঠনিক চিন্তা করতে হবে। শুধু রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্দেশ করলেই হবে না, সেই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যে শক্তি দরকার তার জন্য সাংগঠনিক চিন্তা করতে হবে। এবং সংগঠন গড়ে তোলার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি সময় এটা দিতে হবে। ধন্যবাদ।