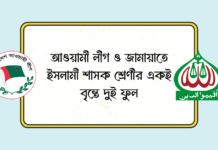১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে দিল্লি আগ্রা পতনের পর বিদ্রোহের কেন্দ্র হয়ে ওঠে মধ্য প্রদেশের ছোটো রাজ্য ঝাঁসী। ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাইয়ের নেতৃত্বে সেখানে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। লক্ষীবাইয়ের বয়স তখন ছিল কম, ২৩ বছর, কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি বিদ্রোহের মূল নেতৃত্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নেতৃত্বে যোগ্যতাও তিনি প্রমাণ করেছিলেন। রাজরাণী হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ নাগরিক আর সিপাহীদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল প্রবাদতুল্য। ঝাঁসীর নারীদের নিয়ে তিনি নারী বাহিনী গঠন করেছিলেন, নিজেও নিষ্ঠার সাথে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ঝাঁসীতে তিনি প্রবল গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং প্রাণপণ তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি হিউরোজকে রাণীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল। ১৮৫৮ সালের মার্চ থেকে শুরু করে জুন পর্যন্ত সেনাপতি স্যার হিউরোজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে একাধিক যুদ্ধে রাণী বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন, অবশেষে ১৭জুন ১৮৫৮ সাল, ফুলবাগ নামক স্থানে যুদ্ধরত অবস্থায় রাণীর মৃত্যু হয়। রাণীর এই মৃত্যুর সাথে লক্ষৌ মিরাট কানপুর আগ্রা দিল্লি ঝাঁসী সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে বিশাল ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল তারও সমাপ্তি ঘটে।
পরবর্তীতে রাণী সম্পর্কে সেনাপতি হিউরোজ লিখেছেন “রাণীর বংশ গৌরব, সৈনিকগণ ও অনুচরদিগের প্রতি তাঁহার অপরিসীম উদারতা, সর্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তিতে অবিচলিত দৃঢ়তা তাঁহাকে আমাদের প্রভূত ক্ষমতাবান ও ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছিল।”
রাণী লক্ষীবাইয়ের জীবনী নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। ইংরেজি ও ফরাসি ভাষাতেও মহাবিদ্রোহের উপর গবেষণা গ্রন্থ, ফিকশন রচিত হয়েছে। ভারতে সিনেমা হয়েছে একাধিক। বাংলা ভাষায় রজনীকান্ত গুপ্ত ৫ খণ্ডে- সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস নামে অনন্য ইতিহাস গ্রন্থ লিখেছেন, যা ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৭ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার, শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রাণী লক্ষীবাইয়ের জীবনী লিখেছেন। মহাশ্বেতা দেবী খুবই তথ্য বহুল রাণী লক্ষীবাইয়ের জীবনী লিখেছেন যা প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ১৩৬৩ সালে। তিনি রাণী লক্ষীবাইয়ের উত্তর পুরুষ যারা তখনও জীবিত ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কিছু দুর্লভ ছবিও তিনি তাঁর বইয়ে সংযোজন করেছেন। এই বইয়ের তথ্য সূত্রে চন্ডীচরণ মিত্র রচিত ঝাঁসীর রাণী বইয়ের নাম উল্লেখ আছে। যদিও এই বইয়ের কোনো প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। প্রশ্ন হলো কে এই চন্ডীচরণ মিত্র? তিনি কি শ্রীচন্ডীচরণ সেন লিখিত ঝান্সীর রাণী উপন্যাসের কথা বলতে চেয়েছেন? ১৮৭৮ সালে অর্থাৎ সিপাহী যুদ্ধের মাত্র ২০ বছর পর কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেস থেকে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা এই বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়; দাম ২ টাকা। এই বই নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা সমালোচনা কোথাও হয়েছে বলে জানা যায় নি। সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে শ্রীচন্ডীচরণ সেনের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। অতি সম্প্রতি বইটি বাজারজাত হতে দেখা যাচ্ছে।
নানা কারণে আজকের দিনেও উপন্যাটি শুধু প্রাসঙ্গিক না, গুরুত্বপূর্ণও।
২
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলার বিদ্বৎসমাজের তৎপরতা প্রসার লাভ করতে থাকে। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রোধ, ধর্ম সংস্কার ইত্যাদি নানা বিষয়ে বাংলার বিদ্বৎসমাজ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইতিহাস সাহিত্য দর্শনের চর্চা প্রসার লাভ করে এবং বিদেশী মনীষীদের লেখার চর্চা শুরু হয়। বিদেশ থেকে নানা বিষয়ের বই আমদানি শুরু হয় এই সময়ে। কিন্তু রামমোহনের সময় থেকে শুরু করে একেবারে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত বাংলার বিদ্বৎসমাজ রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্নে একেবারে নীরব থেকেছে। দেশটা যে ব্রিটিশ অধিকৃত উপনিবেশ এই বাস্তবতা তাদেরকে কখনও বিচলিত করেনি। যে কারণে ১৮৫৭ সালে সারা ভারতব্যাপী সংঘটিত মহাবিদ্রোহ, কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস যাকে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন, সেই ঘটনাও বাংলার বিদ্বৎসমাজকে কিছুমাত্র আলোড়িত করেছিল বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। দুশো বছরের উপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার অন্তত তিনজন সাহিত্যিক বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে, মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ তাঁদের রচনাতেও উপনিবেশিক শাসনের ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। এই সীমার বাইরে যে শ্রীচন্ডীচরণ সেন এমন নয়, কিন্তু তাঁর রচনায় যে প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় সময় বিচারে সেটাকে ব্যতিক্রমই বলতে হবে।
ঝান্সীর রাণী উপন্যাসে লেখক তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি উপলক্ষে নিজস্ব মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন জোরালোভাবে। ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন ‘পুস্তকখানি উপন্যাসাকারে লিখিত হইলেও ঐতিহাসিক বিবরণ অবিকৃত রহিয়াছে।’ মোটা দাগে কথাটা ঠিক হলেও কাহিনীর প্রয়োজনে তিনি কিছু কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন বা ঘটনার অতিরঞ্জন ঘটিয়েছেন যা তাঁর অভিষ্টকে স্পষ্ট করেছে।
যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ওরফে যোগিরাজ আর নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রী এই দুজনের কথোপকথন উপন্যাসের দীর্ঘ জায়গা জুড়ে আছে। মূলত এই দুজনের কথোপকথনের মাধ্যমেই লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যোগিরাজ যুবক, বাঙালী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। যৌবনে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের কারণে তাঁর প্রিয় ২ বোনের জীবন বিনষ্ট হলে তিনি গৃহ ত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নেন। অতঃপর স্বদেশ পরিভ্রমণে ব্রতী হন। একসময় তিনি নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রীর কন্যা গঙ্গাবাইয়ের পাণিপ্রার্থী হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর রাও কৌশলে গঙ্গাবাইকে অন্তঃপুরবাসিনী করলে সে ইচ্ছা তাঁর অপূর্ণ থেকে যায়। গঙ্গাবাইয়ের পিতা নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রী। তাঁর জীবন শুরু হয় কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অতঃপর নিতান্ত নিম্ন পদের চাকরি থেকে তিনি মোটামুটি উচ্চ পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সৎ আর নির্মোহ জ্ঞানান্বেষী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর ধর্ম বা জাত-পাতের কোনো পরিচয় লেখক কোথাও উল্লেখ করেননি, আহার বিহারেও তাঁর কোনো বাছ-বিচার ছিল না। ঘটনার সময় তিনি বৃদ্ধ, বয়স ৮২, ইংরেজ সরকারের পেনশন ভোগী। গোটা উপন্যাসে তিনি লেখকের মুখপাত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছেন। লেখক নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রীর মুখ দিয়ে নিজের কথাগুলো বলেছেন।
উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় প্রচলিত সংস্কার আন্দোলন সমূহের ব্যাপারে লেখকের তেমন কোনো আস্থা ছিল না। রাজা রামমোহন ছাড়া আর কারো নাম তিনি বইতে উল্লেখ করেননি। এক জায়গায় মাত্র নাম উল্লেখ না করে ‘সংস্কৃত কলেজের এক অধ্যাপক’ এর বিধবা বিবাহের চেষ্টাকে প্রশংসা করেছেন।
ভারতবর্ষের মানুষের শিক্ষাকে কটাক্ষ করে তিনি বলছেন “চিন্তাহীন মনুষ্য কখনও কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে না। এ সংসারে যে সকল মহাত্মা বিষয় বিশেষ শ্রেষ্ঠত্য লাভ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন। সহস্র সহস্র পুস্তক অধ্যায়ন করিলেও চিন্তাহীন লোক কখনও প্রকৃত জ্ঞান উপার্জন করিতে সমর্থ হয় না। ইহার একটা প্রধান দৃষ্টান্তস্থল ভারতের বর্তমান অবস্থা।” (৪১) এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলছেন “সংসারের অধিকাংশ লোকই জ্ঞানাভিমানী, জ্ঞান পিপাসু নহে। এ সংসারে জ্ঞান পিপাসুদের সংখ্যা অতি অল্প। শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত যুবকগণকে প্রায়ই জ্ঞানাভিমানী দেখা যায়। ইহারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের পর মনে করেন যে বিশ্বসংসারে এমন বিষয় এমন শাস্ত্র নাই যাহা ইহাদিগের অবিদিত রহিয়াছে। ইহাদের এই জ্ঞানাভিমানই মানসিক অরুচি এবং মানসিক জড়তা উৎপাদন করিয়া মনের জ্ঞান পিপাসা বিনাশ করে।”(৫৫) এই শিক্ষিত বাঙালী সম্পর্কে লেখক যে উচ্চ ধারণা পোষণ করবেন না সেটাই স্বাভাবিক। “তোমাদের বাঙ্গালিদিগের কেবল বক্তৃতা শক্তিটাই কিছু অধিক। বাঙ্গালিরা দেশের খবর বড় রাখেন না, দেশের খবর তাহাদিগের জানিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালিদের যে অদ্ভুত বক্তৃতা শক্তি, যে বিষয়ে তাহারা কখনও চিন্তা করেন নাই, যে বিষয়ে তাহারা কিছু জানেন না, সে বিষয়েও তাহারা অনায়াসে চারিঘন্টা বক্তৃতা করিতে পারেন। বিষয়ের অভাব হইলেও তাহাদিগের বাক্যের অভাব হয়না, চিন্তার অভাব হইলেও তাহাদিগের শব্দের অভাব হয়না।” (১১৫)
উনবিংশ শতকের সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে লেখক ছিলেন নির্লিপ্ত। তিনি বলছেন “যে দেশে অসাধুতা, এবং বিশ্বাসঘাতকতা পুরস্কৃত হয়, যে দেশে তোষামোদ, কপটাচরণ, নীচাশয়তা এবং আত্মহীনতা প্রশংসিত হয়; যে দেশে কাপুরুষতা এবং ভীরুতা সমাদৃত হয়; যে দেশে স্বদেশানুরাগ এবং সাধারণের মঙ্গলেচ্ছা সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ; যে দেশে স্বাধীনতার ভাব অঙ্কুরিত হইবামাত্র সমূলে উৎপাটিত হয়; সে দেশে-কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি ধর্ম সম্বন্ধীয়, কোন প্রকার সংস্কার কার্য্য-কোন প্রকার উন্নতিই-সম্ভবপর নহে।” (২৩৩) বলা বাহুল্য, উনবিংশ শতকের সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ছিল মূলত হিন্দু উচ্চ বর্ণের মধ্যে সীমিত। হিন্দু নিম্ন বর্ণ বা বৃহত্তর মুসলমান সমাজের সাথে এই আন্দোলনের তেমন কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। লেখক এই আন্দোলনকে কটাক্ষ করেছেন। সমাজ সংস্কার সম্পর্কে সে আমলে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন আজকের দিনেও সেটা খুবই প্রাসঙ্গিক- “ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের অন্তরস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গুণরাশি বিকশিত হইবার পথ না পাইলে, সমাজ সংস্কার কখনও সম্ভপর নহে। বিবিধ প্রকার লোক দ্বারা সমাজ গঠিত হইয়াছে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ সদগুণ বিকশিত হইলেই সমাজের উন্নতি হয়।” (১৪৫)
পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে হিন্দু ধর্মের প্রচলিত কুসংস্কারে বিদ্দিষ্ট হয়ে যোগিরাজ নিজের ব্রাহ্মণ ধর্ম ত্যাগ পূর্বক ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যোগিরাজ বলছেন “মানুষ সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব বর্জিত না হইলে, একবারে আশ্রয়হীন না হইলে কখনও হিন্দু সমাজে তিষ্টিতে পারে না,”(২০৭) অধিকন্তু “হিন্দু সমাজ সত্যই হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ অরণ্য” (২২১)।
কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কেও যে লেখক আস্থার মনোভাব পোষণ করেছেন এমন নয়। লেখকের মুখপাত্র নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রীর কথায় “আমি পূর্বে মনে করিতাম যে তোমাদের বঙ্গদেশের ব্রাহ্ম সমাজেরা ভীরু হইলেও জ্ঞান চর্চার বিরোধী নহেন। কিন্তু এখন দেখি তোমাদের বঙ্গদেশের সংস্কারকগণ শুদ্ধ কেবল জ্ঞান চর্চার বিরোধী নহেন; তাহারা নারী জাতির উন্নতির বিরুদ্ধেই খড়্গ হস্ত।” (১৪৯) সমাজের আলোচনায় নারী প্রসঙ্গ অনিবার্য। নারীর প্রতি লেখকের যে মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি আজকের যুগে সেটা বিষ্ময়কর বলে মনে হয়- “বঙ্গদেশে প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের মধ্যেই এক প্রকারে না এক প্রকারে নারী হত্যা এবং বালিকা হত্যা হইতেছে। দেশ একেবারে পাপে ডুবিয়া রহিয়াছে। এই নরহত্যাকারী জাতির কখনও স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা নাই।” (৩৪২) এরপরে অন্যত্র নারী সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন সেটাকে স্থান-কাল নিরপেক্ষ বলা যায়- “ভীরুতা যে সর্ব প্রকার পাপের মূল কারণ তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিশেষত সামাজিক কুনিয়ম প্রায় সারা দেশেই নারীদিগকে ভীরুতার দিকে পরিচালন করিতেছে। নারীগণ সকল বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য অধিকার লাভ করিতে না পারিলে এ সংসারে বিবিধ পাপ এবং দুঃখ যন্ত্রণা কিছুতেই নিবারিত হইবে না।” (৩৬০)
১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আবহমানকালের বাঙালী সমাজে অদৃষ্টপূর্ব ভাঙাগড়ার সৃষ্টি করেছিল। এই ভাঙাগড়ার মাধ্যমে নতুন এক অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। সমাজে যার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী, বলা যায় সেই প্রভাব এখনও পর্যন্ত কমবেশি বিরাজমান। নবউত্থিত এই অভিজাত শ্রেণী সম্পর্কে লেখকের মনোভাব ছিল খুবই নেতিবাচক- “ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পনীর রাজত্বের প্রারম্ভে আমাদের দেশের লোকের উপর ঘোর অত্যাচার হইতে লাগিল। তাহাতে প্রাচীন পরিবার সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন বঙ্গদেশের যে সকল ভদ্র পরিবার দেখিতে পান, যে সকল রাজা মহারাজা দেখিতে পান, ইহাদের পিতা পিতামহের মধ্যে কেহ ইংরেজদের বেনিয়ান ছিলেন, কেহ ইংরেজদিগের সরকার ছিলেন, কেহ ইংরেজদিগের মেট-মিস্তিরি ছিলেন। তাহারা প্রায় সমুদয়ই চোর, এবং বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। সেই সকল চোর বিশ্বাসঘাতকের পুত্র পৌত্ররাই এখন রায় বাহাদুর হইতেছেন।” (১৬৫)
হিন্দু ধর্ম, জাতিভেদ প্রথা, সমাজে অভিজাত শ্রেণীর অবস্থান, সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদি নানা বিষয়ে নানাভাবে লেখক বিস্তারিত উল্লেখ করলেও বিষ্ময়ের ব্যাপার মুসলমানদের সম্পর্কে এই বিশাল উপন্যাসে তিনি মাত্র ৪ লাইনে তাঁর কথা শেষ করেছেন, “মুসলমানদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। সাতবার ইংল্যান্ডে গেলেও ওদের কুসংস্কার দূর হয়না। মুসলমান জাত অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত। চিন্তাশীলতা ইহাদের মধ্যে একেবারেই নাই।” (১৬৪)
প্রশ্ন থাকে মুসলমানদের সম্পর্কে এটা কি লেখকের উদাসীনতা? নাকি বিদ্বেষ? না অজ্ঞতা? এই প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কেননা বিশেষত বাংলায়, অধিবাসিদের প্রায় অর্ধাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও উনবিংশ শতকের সমাজপতিরা বৃহত্তর বাঙালী সমাজ থেকে মুসলমানদের খারিজ করে নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিল। যার দায় অদ্যাবধি এ দেশের মানুষ বহন করে চলছে।
৩
প্রশ্ন হতে পারে ঝান্সীর রাণী উপন্যাসের জন্য যে বিস্তৃত পটভূমির অবতারণা লেখক করেছেন সেটার অনেক কিছুই অপ্রাসঙ্গিক কিনা? লক্ষ করার বিষয় লেখক এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে কারণে আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও গুরুত্বের দিক থেকে বিষয়গুলো উপেক্ষা করা যায় না। সিপাহী বিদ্র্রোহের ঘটনাকে তিনি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখেননি, অনেক ঘটনার প্রতিফল হিসেবে দেখতে চেয়েছেন।
লেখক বলছেন “বর্তমান সিপাহী বিদ্রোহের বীজ ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই অঙ্কুরিত হইতেছিল। কিন্তু তৎপ্রতি এ পর্যন্ত কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই। এখন সেই বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবা মাত্র চতুর্দ্দিক হইতে আহুতি পড়িতে লাগিল। যে সকল লোক এ পর্য্যন্ত নিতান্ত নিশ্চেষ্ট অবস্থায় জড়ের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছিল আজ তাহারাও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহাদের অন্তরেও বীরত্বের সঞ্চার হইল।”(৬৮)
এতদসত্ত্বেও সিপাহীদের উপর তিনি যে খুব আস্থা দেখিয়েছেন এমন না। সিপাহীদের ইংরেজ নারী ও শিশু হত্যাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। অপরদিকে ইংরেজদের মধ্যে তিনি অনেক ভালো মানুষের সন্ধান পেয়েছেন, যেমন সেনাপতি স্যার হেনরি লরেন্স, যিনি যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তাছাড়া শাসক হিসেবে বেটিঙ্ক, তাঁর উপদেষ্টা মেটকাফ মেকলেকে তিনি প্রশংসা করেছেন। আবার ইংরেজদের প্রতি ঘৃণাও যে তিনি কম দেখিয়েছেন এমন না। রাণী লক্ষীবাইয়ের জবানীতে তিনি বলছেন “ইংরেজরা অত্যন্ত পাপাচারী এবং নিষ্ঠুর। কোন প্রকার কুকার্য্যই তাহাদিগের অসাধ্য নহে। ইংরেজ শূকরের ধর্ম্মা ধর্ম্ম একেবারে নাই।” (৩৪৭)
উত্তর আর মধ্য ভারতের যেসব অভিজাত সামন্ত এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে এসেছিল, ইতিহাসে যাদের অনেকেই বিদ্রোহের বীর হিসেবে খ্যাত, তাঁদেরকে লেখক কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি; যেমন নানা সাহেব, রাও সাহের, বান্দার নবাব প্রমুখ, এমন কি দিল্লির বাদশাহ। লেখক বলছেন এরা সব ইংরেজদের বখরা খোর। শাসক হিসেবে এরা অথর্ব, যোদ্ধা হিসেবে অদক্ষ, নিজেদের মধ্যে সম্পর্কও এদের ভালো না। বখরায় কম পড়ে যাওয়াই এদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কারণ। কাজেই বিদ্রোহে নেতৃত্বের বিষয়ে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলছেন “স্বাধীনতা শব্দের অর্থ কি? আমাদের স্বদেশের একজন রাজা হইলেই কি আমরা স্বাধীন হইব? আমাদের দেশের একজন দস্যু ভারতবর্ষের রাজা হইয়া যদি সমুদয় ভারতবাসিদিগের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করেন তবে কি আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিব?” (১৫১)
প্রায় দুই বছর ধরে ভারত জুড়ে এই বিদ্রোহের রেশ চলেছিল। বিদ্রোহের কারণগুলো লেখক তখন দক্ষতার সাথে চিহ্নিত করেছিলেন। প্রথমতঃ করবৃদ্ধি। অযোধ্যা রাজ্য অর্ধেক ইংরেজরা হস্তগত করেছিল কিন্তু তাদের প্রাপ্য করের পরিমাণ ঠিকই ছিল। কাজেই অতিরিক্ত কর আদায়ের জন্য অযোধ্যার নবাবকে জনগণের উপর করের বোঝা দ্বিগুণ করতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থা ছিল গণবিরোধী। কেউ কখনও বিচার প্রার্থী হলে তাকে একেবারে সর্বস্বান্ত হতে হত। তৃতীয়তঃ ইংরেজরা দেশীয় লোকদের শাসন বিভাগে বা সৈন্য বিভাগে উচ্চ পদ প্রদান করতো না। চতুর্থতঃ দেশীয় লোকদের প্রতি ইংরেজদের ছিল চরম অবিশ্বাস। লক্ষ্য করার বিষয়, ইংরেজ কর্তৃক ধর্ম নাশের আশঙ্কাকে সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান কারণ হিসেবে প্রচার আছে। লেখক কিন্তু বিষয়টাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি।
এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে লেখক বলছেন- “জমিদার কৃষকদের সর্বনাশ করিতে চেষ্টা করেন, প্রজা জমিদারদের প্রবঞ্চনা করিতে একটুও ত্রুটি করে না। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে ঘৃণা করেন, মুসলমানরা আবার হিন্দুদিগের নির্যাতন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং দেশের সমগ্র প্রজা গভর্ণমেন্টের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেও এ পর্যন্ত তাহারা সকলেই নির্বাক ছিলেন। এখন অকষ্মাৎ মিরাটের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইবা মাত্র অর্থাৎ এক দিক হইতে আগুন জ্বলিয়া উঠিবা মাত্র চতুর্দিক দিক হইতে সকলেই সে আগুনে আহুতি প্রদান করিতেছেন।” (১২৪) সন্দেহ নেই, একটা গণআন্দোলন কিভাবে উজ্জিবিত আর সংগঠিত হয় সেটা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে লেখক যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন সেটা সত্যিই বিস্ময়কর।
উপন্যাসে নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রী মহারাষ্ট্রের বীর তান্তিয়া তপি (তাঁতিয়া টোপি)-র উপদেষ্টা। যুদ্ধে যে সিপাহীদের পরাজয় হবে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। কারণ হিসেবে তিনি বলছেন, প্রথমতঃ ইংরেজরা জ্ঞানেতে নীতিতে বীরত্বে এবং সভ্যতাতে ভারতীয়দের থেকে শতগুণে শ্রেষ্ঠতর। দ্বিতীয়তঃ এদেশের লোকদের ইংরেজদের মতো রাজ্য শাসনের দক্ষতা নেই। তৃতীয়তঃ বিদ্রোহের শত শত কারণ থাকা সত্ত্বেও ধর্মনাশের আশঙ্কাকে বিদ্রোহের কারণ হিসেবে সামনে আনা হচ্ছে। চতুর্থতঃ ইংরেজদের বীরত্ব। সিপাহীরা ইংরেজদের মতো বীরত্ব দেখাতে পারছে না। তথাপি লেখকের মতে এই বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত। ইংরেজদের চরম দুঃশাসনের প্রতিবাদে বিদ্রোহের বিকল্প নেই। তান্তিয়া তপিকে তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন “এখন প্রকৃত বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জন করিলে, তোমার মৃত্যু দ্বারা দেশের এবং ভাবী বংশধরগণের বিশেষ উপকার হইবে।”(১৭৮)
লক্ষ্য করার বিষয় এই উপন্যাসে বিপুল চরিত্রের সমাবেশ ঘটলেও একমাত্র ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাই আর তান্তিয়া তপি ছাড়া আর আর কাউকেই লেখক তেমন প্রাধান্য দেননি। ছোটোবেলা থেকেই লক্ষীবাই ছিলেন মাতৃহীন। কোনো সামন্ত পরিবার থেকে তাঁর উত্থান হয়নি। তিনি ছিলেন সপ্রতিভ, বাল্যকালেই অস্ত্র শিক্ষা নিয়েছিলেন। ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সাথে যখন তাঁর বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স ছিল সাড়ে সাত বছর, গঙ্গাধর রাওয়ের ২৯ প্রায়। রাজা ছিলেন ইংরেজের পেনশনজীবী, ভোগী, নারীলোলুপ। রাণী লক্ষীবাই তাঁর সহজাত গুণে প্রাসাদে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তারা ছিলেন নিঃসন্তান। রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু হলে ইংরেজরা তাঁর পেনশন বন্ধ করে দেয় এবং রাজার করা ঋণ পরিশোধের জন্য রাণীর উপর চাপ দিতে থাকে। তখন থেকেই রাণীর সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব শুরু হয় । এতদসত্ত্বেও রাণী কখনও বিদ্রোহের কথা ভাবেন নি। বারংবার তিনি সমঝোতার প্রস্তাব পাঠান ইংরেজদের কাছে, কিন্তু কোনো সন্তোষজনক সাড়া পাননি। ইতোমধ্যে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং রাণীর উপর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। সম্মত না হয়ে রাণীর উপায় ছিল না। সম্ভবত রাণীর মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ আগে থেকেই ছিল। ইতিহাস বলে, রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর রাণী নিজ উদ্যোগে ৫টা কামান মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিল। পরে যেগুলো বিদ্রোহীদের কাজে লাগে।
তান্তিয়া তপি মহারাষ্ট্রের সৈনিক। সৈনিক হিসেবে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রবাদতুল্য। কিন্তু ইংরেজদের বৈষম্য নীতির কারণে সেনাবাহিনীতে তাঁর যোগ্য পদোন্নতি হয়নি। যেহেতু সব রকম সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বঞ্চিত সেহেতু বিদ্রোহ করার ন্যায় সঙ্গত অধিকার তাঁর আছে। এই ছিল তান্তিয়া তপির উপদেষ্টা নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রীর অভিমত। তবে বিদ্রোহে যে ব্যাপক জনগণ তথা কৃষকের অংশগ্রহণ ছিল সে দিকে লেখকের দৃষ্টি তেমন ছিল বলে মনে হয় না, যদিও ইংরেজদের ভয়ংকর নৃশংসতা থেকে যে সাধারণ নারী পুরুষ শিশু কেউ বাদ যায়নি সে বিষয়টা জোরালোভাবেই এসেছে।
উপন্যাসে খল চরিত্র বানানো হয়েছে আজিমুল্লাহকে। যতোদূর জানা যায় ইংরেজরা নানা সাহেবের পেনশন হ্রাস করলে স্থানীয়ভাবে নানারকম দেনদরবার করেও যখন কাজ হয়নি তখন আর্জি নিয়ে আজিমুল্লাহকে লন্ডনে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে আজিমুল্লাহ ব্যর্থ হয় অতঃপর তিনি দেশে না ফিরে ইউরোপের যেসব দেশে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছিল সেরকম কিছু দেশ সফর করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং দেশে ফিরে সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠনের চেষ্টা করে। লেখক কেন উপন্যাসে তাঁকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বোঝা যায় না। ফুলবাগের যুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় রাণী নিহত হন। তান্তিয়া তপি পশ্চাদপসরণ করেন। পরবর্তীতে ধৃত হলে ইংরেজরা কামানের গোলার মুখে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করে।
ঝাঁসীর রাণী আর তান্তিয়া তপির ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাসে কিছু রোমান্টিক গুঞ্জন আছে। সাহিত্যিক হিসেবে লেখক রাণীর এক উক্তির মাধ্যমে প্রসঙ্গের সুন্দর সমাধান দিয়েছেন, “তান্তিয়ার প্রেম আমাকে পরাস্ত করিতে উদ্যত হইলেই আত্মাভিমান, অহঙ্কার, আত্মসমাদর এবং পূর্ব সংস্কারকে আর হৃদয় হইতে পলায়ন করিতে দিব না। এ সংগ্রামে এই কয়েকটি সৈন্যই মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করিবে। ইহারাই আমার বিশ্বস্ত শরীর রক্ষক হইবে।” (৩৭২)
আজ থেকে ঠিক দেড়শ বছর আগে লিখিত বিশাল উপন্যাস ঝান্সীর রাণী উপন্যাস হিসেবে কতটা সফল সে বিচার পাঠকের। যে ফর্মে উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য কিনা সে প্রশ্নও উঠতে পারে। কিন্তু ঝান্সীর রাণী উপন্যাসকে কেন্দ্র করে লেখক ভারতের তথা বাংলার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির যে বিশাল প্রেক্ষিত রচনা করেছেন সেটা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। লেখক হিসেবে সাহিত্যগুণ অপেক্ষা সামাজিক দায়কেই তিনি যেন অধিক প্রশ্রয় দিয়েছেন। প্রচলিত বিশ্বাস আর সংস্কারের বাইরে লেখক তাঁর মৌলিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন সমগ্র উপন্যাস জুড়ে।
চন্ডীচরণ সেন (১৮৪৫ – ১৯০৬) ব্রিটিশ সরকারের অধীনে বিচারকের চাকরি করতেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনুবাদ টমকাকার কুটীর (১৮৮৫) বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। মহারাজ নন্দকুমার (১৮৮৫), অযোধ্যার বেগম (১৮৮৬) প্রভৃতি তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক উপন্যাস। মহারাজা নন্দকুমার উপন্যাসের জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত কবি কামিনী রায় ছিলেন তাঁর জেষ্ঠ্যা কন্যা।
(পাভেল চৌধুরী কথাসাহিত্যিক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)