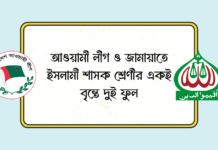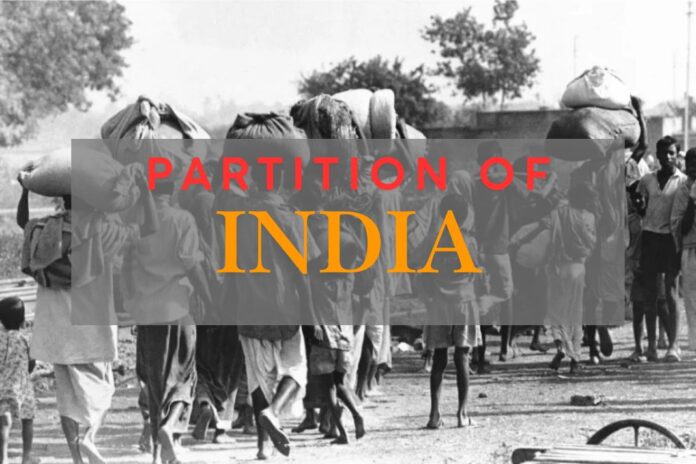ভারতের ইতিহাসের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, হাজার হাজার বছর ধরে বাইরে থেকে বিশাল আকারে বিভিন্ন জাতির লোক যেভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে এ রকম অন্য কোন দেশে হয় নি। এই বিদেশীরা ভারত আক্রমণ ও লুটপাট করে নিজেদের দেশে ফিরে যায় নি। তারা এদেশে এসে থেকে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল তিনটি, গ্রীসের আলেকজান্ডার, গজনীর মাহমুদ এবং ইরানের নাদির শাহ্। কিন্তু সামান্য ব্যতিক্রম সত্ত্বেও বলা যায় যে, আক্রমণকারী এই বিদেশীরা এদেশ লুটপাট করে ফিরে যাওয়ার জন্য ভারত আক্রমণ করে নি। মধ্য এশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এসেছিল এবং বিপুল সংখ্যায় ভারতে থেকে গিয়েছিল। সুদূর প্রাচীন কালে যে আর্যরা ভারত আক্রমণ করে এদেশে এসে বসবাস শুরু করেছিল সেই বিদেশীরাই পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির মূল নির্মাতা। আর্যদেরকে বাদ দিয়ে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি চিন্তাই করা যায় না। আর্যদের পর ধারাবাহিকভাবে শক, হূণ থেকে নিয়ে আরব, ইরানী, তুর্কী, পাঠান মোগল পর্যন্ত ভারতে এসেছে এবং এখানে থেকে গেছে।
উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইউরোপীয়রা সেসব দেশ দখল করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেও তার সাথে ভারতে বিদেশীদের বসবাস ছিল একেবারে অন্য রকম। ইউরোপীয়রা আমেরিকার আদিবাসীদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে প্রায় নিশ্চিহ্ন ও একঘরে করেছিল। নোতুন আমেরিকার শাসন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের কোন অবস্থান থাকে নি। তাছাড়া তাদের থেকে ইউরোপীয়দের সংস্কৃতি ছিল অনেক উচ্চ স্তরের। আর্যরা ভারতে এসে যে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস করেছিল সেটা ছিল আর্যদের সভ্যতা থেকে অনেক উচ্চ স্তরের। আর্যরা ছিল পশুপালক ও যাযাবর। তাদের সংস্কৃতি ছিল মূলতঃ পশু পালকদের সংস্কৃতি যার সাথে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। যদিও তা ঘটতে সময় লেগেছিল। এমনভাবে এই সংমিশ্রণ ঘটেছিল যাতে আর্য সভ্যতা পরিণত হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতায়। বলতে গেলে এখন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল আর্যদের দ্বারা। এক হিসাবে বলা চলে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্যপূর্ব ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকে অনেকাংশে আত্মসাৎ করেছিল। ভারতের হিন্দু সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় সেটা বিদেশী আর্যরাই নির্মাণ করেছিল।
আর্যদের পর শক, হূণ, আরব, ইরানী, তুর্কী, পাঠান, মোগলরা ভারত আক্রমণ ও দখল করেছে এবং ভারতে থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তারা এক দেহে লীন হয়েছে। এভাবে বহিরাগতরা ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকার সময় তারা ভারতীয় জনগণকে শত্রু মনে করে তাদের থেকে নিজেদেরকে একেবারে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করে নি। উপরন্তু নিজেদের অবস্থান মজবুত করার জন্য তারা ভারতীয়দের সাথে যথাসাধ্য একাত্ম হতে চেষ্টা করেছে। তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করে ঐক্যের মধ্যেই নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মঙ্গল দেখতে চেয়েছে।
আরব, তুর্কী, পাঠান, মোগল ইত্যাদি যে সব জাতি ভারতে এসেছিল এবং এদেশ শাসন করেছিল তাদের সাথে অবশ্য পূর্ববর্তী প্রবেশকারীদের একটা বড় পার্থক্য ছিল। ভারতে থেকে ভারতীয় হয়ে গেলেও তারা নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করে নি তাদের পূর্ববর্তীদের মত। তারা ছিল ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং এদিক দিয়ে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকলেও ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম উভয়েই পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই প্রভাব উল্লেখযোগ্য ছিল।
ধর্মীয়ভাবে স্বতন্ত্র হলেও মুসলমান শাসকরা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে নিজেদের অবস্থান নিরাপদ ও শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। প্রথমে সুলতানী আমল ও পরে মোগল পাঠান আমলে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। আলাউদ্দীন খিলজী ও পরে আকবর সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনেই ইসলাম ধর্মের সাথে নিজেদের সম্পর্ক শিথিল করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন তৈরী করতে চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি আওরঙ্গজেব হিন্দু বিদ্বেষী হলেও এবং কিছু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করলেও তিনি আবার অনেক হিন্দু মন্দিরে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন এবং তাঁর প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে হিন্দুরা ছিলেন। হিন্দু মুসলমানকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার কোন চেষ্টা আওরঙ্গজেবের ছিল না। মোগল আমলের শেষ পর্যন্ত এই নীতি অব্যাহত ছিল।
ইউরোপে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটতে থাকার সময় থেকে, বলা চলে সতেরো শতক থেকে, ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্য আসতে থাকে। আঠারো শতকে তারা ভারতে নিজেদের খুব শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলে। এর মধ্যে ইংরেজরাই ছিল প্রধান এবং ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে তারা বাণিজ্যের প্রয়োজনেই নিজেদের সামরিক শক্তি গড়ে তোলে। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের কারণেও এভাবে সামরিক শক্তি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। এদিক দিয়ে ইংরেজ এবং তার সাথে ফরাসীরাই ছিল অগ্রগণ্য।
আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে মাদ্রাজ ও বাঙলায় ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্যিক কুঠিকে কেন্দ্র করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে তার জোরে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সম্প্রসারিত করতে থাকার সময় বাঙলায় নবাবী শাসনের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে, মাঝে মাঝে সামরিক সংঘর্ষ হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা স্বাধীন নবাবকে পরাজিত করে তাদের তাবেদার নবাবদেরকে একের পর এক ক্ষমতায় বসিয়ে বাঙলা শাসন করতে নিযুক্ত হয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাঙলায় ও পরে ভারতের অন্যান্য কিছু অঞ্চলে নিজের সরাসরি শাসন প্রবর্তন করে, যে শাসন ১৮৫৭ সালে সিপাহী অভ্যুত্থান পর্যন্ত বজায় ছিল। সিপাহী অভ্যুত্থানের পর ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীর শাসন উচ্ছেদ করে ভারতে সরাসরি নিজের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।
ব্রিটিশ পূর্ববর্তী যে জাতিরা ভারতে এসেছিল তারা এদেশে বসবাসের উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল। তারা ভারতে থেকে গিয়েছিল স্থায়ীভাবে। কিন্তু ইউরোপীয়দের ভারতে আসার উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম। তারা এসেছিল বাণিজ্যিক মুনাফার স্বার্থে। ইংরেজরা যখন বাঙলায় ক্ষমতা দখল করে সে সময়টা ছিল ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার সময়। তারপর বাঙলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল পরিণত হয় ইংল্যান্ডের উৎপাদিত শিল্প পণ্যের বাজারে। শুরু হয় ব্যাপক বাজারী লুণ্ঠন। এই লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হতে থাকে পুঁজি, যা ইংল্যান্ডের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বড় আকারে অবদান রাখে।
১৭৫৭ সালে বাঙলায় ক্ষমতা দখলের পর ইংরেজরা নিজেদের কর্তৃত্বাধীন প্রশাসন গঠন করতে নিযুক্ত হয়। তারা ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন করে বাঙলায় প্রবর্তন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্ত শুধু অর্থনীতি ক্ষেত্রে নয়, বাঙলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। বলা চলে, ঊনিশ শতকে অনেকাংশে এই ব্যবস্থার অধীনেই গড়ে ওঠে এক নোতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, পরবর্তী কালে যারা আরও সুগঠিত হয়ে শুধু বাঙলা নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতের রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে তারা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে তার আধুনিকীকরণ ঘটায়। প্রথম দিকে, ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ফার্সী প্রশাসনিক ভাষা থাকলেও উনিশ শতকের গোড়া থেকেই তারা ইংরেজী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে।
ইংরেজ কোম্পানীর শাসনে ইংরেজী শিক্ষা থেকে নিয়ে অন্যান্য যেসব সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হলো হিন্দুরা তা পুরোপুরি গ্রহণ করলো। তবে মুসলমানরা বিভ্রান্তিবশতঃ নবাবী মোগল শাসনকে নিজেদের শাসন মনে করে তার অবসানের পর ইংরেজ শাসনকে বৈরী শাসন মনে করে তাদের দ্বারা সৃষ্ট সুযোগ সুবিধা ও সেই সাথে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে অনাগ্রহী হয়। ইংরেজ পূর্ববর্তী শাসনে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানসহ অনেকে প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে চাকরী করতো। সেটাই ছিল তাদের অবস্থানের শ্রেণীগত ভিত্তি। সেই ভিত্তি অপসারিত হওয়া এবং মোগল ও নবাবী আমলেও ভূস্বামী ও জমিদার হিসাবে তাদের কোন অবস্থান না থাকায় তারা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। তারা বিপুল সংখ্যায় গরীব হয়ে যায়। তার ওপর ইংরেজ শাসনে ইংরেজী শিক্ষা ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বর্জন করায় তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়। হিন্দুদের থেকে শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে তারা অনেক পিছিয়ে পড়ে।
মুসলমানদের এই পিছিয়ে পড়া অবস্থা একশো বছর ধরে চলার পর সিপাহী অভ্যুত্থানের পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানরা উপলব্ধি করে যে, ইংরেজদের শিক্ষাদীক্ষা বর্জন করা ছিল বড় রকম ভ্রান্তি। এই ভুল সংশোধন করতে তারা উদ্যোগী হলো। এ সময় ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক সরকারের শাসন। তারা মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি মনোযোগ দেয়, কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে। তাদের কিছু কর্ম সংস্থানও হতে থাকে।
হিন্দুরা এতদিন প্রায় নিরঙ্কুশভাবে শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছিল। এরপর মুসলমানরা এক্ষেত্রে আবির্ভূত হলে তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়। হিন্দুরা মনে করে তারা এতদিন যে সুযোগ সুবিধা একচেটিয়াভাবে ভোগ করে আসছিল তার পরিবর্তে তাদেরকে প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হতে হচ্ছে, তাদের ভাগ থেকে একটা অংশ মুসলমানদেরকে দিতে হচ্ছে।
এর ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের একটা দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। হিন্দু জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব এই সময়ে। ষাটের দশকে নব গোপাল মিত্র ও রাজ নারায়ণ বসুর নেতৃত্বে হিন্দু মেলা নামে এক সম্মিলনীর আয়োজন হয় যেখানে ঘোষণা করা হয় যে, হিন্দুরা এক স্বতন্ত্র জাতি। এই জাতিতত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদেরকে মুসলমান থেকে পৃথকভাবে উপস্থিত করা। পরে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে দাঁড়ালেন এই জাতিতত্ত্বের এক প্রবল প্রবক্তায়। মুসলমান সমাজের নেতা হিসাবে বাঙলায় নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী এবং উত্তর প্রদেশে স্যার সৈয়দ আহমদ আবির্ভূত হন। তাঁরা মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে দেন দরবার করেন। এই চেষ্টা করলেও তাঁরা অবশ্য মুসলমানদেরকে কোন পৃথক জাতি হিসাবে উপস্থিত বা ঘোষণা করেন নি। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সময়েই মুসলমানদের দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রথম সূত্রায়িত হয়।
ঊনিশ শতকে ‘সাম্প্রদায়িকতা’ শব্দটির প্রচলন হয় নি। বিশ শতকে ব্রিটিশরাই হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বকে প্রথম সাম্প্রদায়িক হিসাবে আখ্যায়িত করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা শব্দটির প্রচলন না হলেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ নিহিত ছিল। পরে হিন্দু মুসলমানের এই প্রতিযোগিতা ও রেষারেষি বিশ শতকের গোড়া থেকেই বিকশিত হয়ে তিরিশ চল্লিশের দশকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু তাই নয়, রাজনীতির এক নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।
এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিতভাবে ব্রিটিশ সরকার চেষ্টা করে। সিপাহী অভ্যুত্থানের পর মুসলমানদেরকে শিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং তাদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতা করার পর্যায়ে উঠিয়ে এনে তাদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি। তাদেরকে বিভক্ত করে নিজেদের শাসন অনেকটা বিপদমুক্ত ও মসৃণ করার চিন্তা থেকেই তারা এই নীতি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তাদের এক উপায় হয় ইতিহাস চর্চা। বিখ্যাত পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ জেমস মিল তাঁর বিখ্যাত বই The History of India– তে ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ, এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম দুই কাল পর্বকে ধর্মের ভিত্তিতে নামকরণ করলেও ব্রিটিশ শাসনকে খৃস্টান না বলে তিনি ব্রিটিশ আখ্যা দেন। আগে ব্রিটিশপূর্ব ভারতের ইতিহাসকে এভাবে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার ব্যাপার না থাকলেও জেমস মিল একজন সাম্রাজ্যবাদী ও ইতিহাসবিদ হিসাবে সেটা করে ভারতে সাম্প্রদায়িক চিন্তার বিকাশ ঘটানোর শর্ত সৃষ্টি করেন। তাঁর এই চেষ্টা বিফল হয় নি। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয়রা যে ইতিহাস চর্চা করেছিলেন সেটা অনেকাংশেই জেমস মিল এর দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে গঠিত হয়েছিল এবং ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল।
ঊনিশ শতকের বাঙলায় হিন্দু মুসলমানের আপেক্ষিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য বিশ শতকের রাজনীতিতে সংকট সৃষ্টি করেছিল। এজন্য ঊনিশ শতকের অবস্থা পর্যালোচনা ও বিবেচনা ছাড়া বিশ শতকের রাজনীতি বোঝা সম্ভব নয়। ঊনিশ শতকে চাকরীর জন্য হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছিল বিশ শতকে তার সাথে যুক্ত হয়েছিল ক্ষমতার জন্য পুঁজিবাদীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও রেষারেষি। এর পরিণাম ঘটেছিল ভারত ভাগের মধ্যে।
পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। এই সংঘাত যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ও যুদ্ধ বাধায়। কিন্তু কোন দেশের অভ্যন্তরে পুঁজির বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সৃষ্টি করে না। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চলেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে। কোন দেশের নিজেদের পুঁজির বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ছিল না। কিন্তু ভারতে হিন্দু ও মুসলমান পুঁজি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব ছিল। এর ফলে পুঁজির সংঘর্ষের একটা রূপ ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশে দেশে ছিল যুদ্ধ আর ভারতের অভ্যন্তরে ছিল দাঙ্গা। দাঙ্গার ভূমিকা ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হতে সময় লেগেছিল। ১৯২৭ সালের আগে রাজনৈতিক দলগুলো স্বাধীনতার দাবী করে নি। তার পর স্বাধীনতার যে সংগ্রাম শুরু হলো সেটা ব্রিটিশ সরকারকে শত্রু নির্ধারণ করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ছিল না। সেটা ছিল ভারতে ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তাদের ওপর চাপ সৃষ্টির মত। এমনকি অনেকটা আবেদন নিবেদনের মত যাকে মৌলানা মহম্মদ আলী বলেছিলেন Begging and Praying Politics।
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐক্য ছিল না। বিশেষ করে তিরিশের দশক থেকে তা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। এর ফলে ব্রিটিশ বিরোধিতা যতটা ছিল তার থেকে অনেক বেশী ছিল হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধিতা। এ বিরোধিতার কারণেই শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগ হয়েছিল। ভারত ভাগে হিন্দু মুসলমান, কংগ্রেস লীগ উভয়েরই অবদান ছিল।
স্বাধীনতা আন্দোলনের চরিত্র আপোষমুখী ও চাপ সৃষ্টির আন্দোলন হওয়ায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কারও মধ্যে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতা ছিল না। ‘আন্দোলন’ ও আপোষ আলোচনার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছিলো। আন্দোলন যাতে সরাসরি সংঘর্ষের পথে না যায় এজন্য গান্ধী অহিংসার প্রচারক হয়েছিলেন। অহিংস আন্দোলন ছিল তাঁদের রাজনীতির মূল ধারা। অন্য দিকে মুসলিম লীগের সাথেও তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতা ও সশস্ত্র লড়াইয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। চল্লিশের দশকে তারা ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’ আওয়াজ তুলেছিল। কিন্তু তাদের সে লড়াই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল হিন্দু ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।
লক্ষ্য করার বিষয় ছিল যে, গান্ধীর অহিংসা শুধু প্রযোজ্য ছিল ভারতীয়দের ক্ষেত্রে। তারা যাতে আন্দোলনের সময় কোন ধরনের সহিংসতা না করে এটাই ছিল তাঁর অহিংসার আদর্শের মূল কথা। কিন্তু ব্রিটিশের সহিংসতার কোন বিরোধিতা তাঁর মধ্যে ছিল না। চৌরিচৌরার সহিংসতার তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগের ব্রিটিশ সহিংসতার সময় তিনি তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না করে বিস্ময়করভাবে নীরব ছিলেন, যা দেখে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। গান্ধী পেশোয়ারে কিসসাখানি বাজারের ঘটনার সময় ভারতীয় সৈন্যদের দেশপ্রেমমূলক ব্রিটিশ বিরোধিতা এবং জনগণের ওপর গুলি না চালানোর জন্য তাদের সমালোচনা করেছিলেন। গান্ধী ভগৎ সিং এর কার্যকলাপের বিরোধী ছিলেন এবং ব্রিটিশরা তাঁকে ফাঁসি দিলে তার বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রতিবাদ না করে নীরব ছিলেন।
ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের চরিত্র মূলতঃ ছিল সাংবিধানিক। শ্রেণীগত কারণে গান্ধী জিন্নাহ্ উভয়েই আন্দোলন সংসদীয় কাঠামোর মধ্যে আটকে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। মুসলিম লীগ তো প্রকৃতপক্ষে কোন সময়ে ব্যাপক সরকার বিরোধী আন্দোলন কখনো করে নি। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অহিংস আন্দোলন করে আন্দোলনকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতো। কখনো সখোনো আন্দোলন সহিংস আকার ধারণ করলে বা তার সম্ভাবনা দেখা দিলে গান্ধী হস্তক্ষেপ করে তা থামিয়ে দিতেন।
কংগ্রেস লীগের স্বাধীনতা আন্দোলন চলা কালে তারা সব সময়েই ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখতো এবং তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করতো। এই আলাপ আলোচনা চল্লিশের দশকে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছিল। ভাইসরয় এর সাথে আলোচনা, সিমলা সম্মেলনের মতো মতবিনিময় সভা, কেবিনেট মিশনের সাথে আলাপ আলোচনা এবং মাউন্ট ব্যাটনের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা হয়েছিল।
চল্লিশের দশকে কংগ্রেস লীগের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীনতার থেকে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা ও বখরা ভাগের আলোচনা অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৪৪ সালে গান্ধী জিন্নাহ্র মধ্যে আপোষ মীমাংসার জন্য যে দীর্ঘ আলোচনা বেশ কয়েক দিনের জন্য হয়েছিল এবং কোন মীমাংসা ছাড়াই শেষ হয়েছিল সেটা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক কেলেঙ্কারী ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। স্বাধীনতা আন্দোলন করতে গিয়ে আসল শত্রু ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিবর্তে কংগ্রেস লীগের মধ্যে এই ধরনের আন্দোলন যেভাবে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল এটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরল ও ব্যতিক্রমী ব্যাপার।
এই ভাগ বাটোয়ারার দ্বন্দ্বে আসল শত্রু ব্রিটিশ সরকার অনেকটা মধ্যস্থতার কাজ করেছিল! ক্ষমতা হস্তান্তর কিভাবে হবে সেটা শাসক ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস লীগ টেবিলে বসে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করেছিল। এটা ছিল ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে এক চক্রান্তমূলক ব্যাপার। জনগণের মাথায় ঘোল ঢেলে, জনগণের সাথে প্রতারণা করেই তারা ভারত ভাগ করেছিল।
হিন্দু মুসলমান বা কংগ্রেস লীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব এভাবে ভারত ভাগের মত পরিণতি ঘটাতো না এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হতো না, যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাকরণ মেনে ভারতের রাজনীতি অহিংসার নীতি পরিহার করে আন্দোলনকে তার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যেতে দেওয়া হতো। গান্ধী তাঁর ঘোষিত এবং অনুসৃত অহিংস নীতি এবং জিন্নাহ্ তাঁর নীরব অহিংস নীতির মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে দেন নি। এ কারণে সংগ্রামের উত্তাপ সৃষ্টি হলেও সে উত্তাপ ব্রিটিশকে দগ্ধ না করে ভারতীয়দেরকেই দগ্ধ করেছিল। এই প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ রূপ হিসাবে দেখা দিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।
যে কোন আন্দোলন, সংগ্রাম ও যুদ্ধে সঠিকভাবে শত্রু নির্ণয় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটিশ ভারতীয় শাসন উচ্ছেদ ছাড়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু এই সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে ভারতের রাজনীতি বিকশিত হয় নি। ব্রিটিশকে যথার্থ শত্রু মনে না করে তার সাথে আপোষের চিন্তা মাথায় রেখে স্বাধীনতা আন্দোলন করার ফলে যা হবার তাই হয়েছিল। তিরিশের দশকে, বিশেষ করে চল্লিশের দশকে ব্রিটিশের পরিবর্তে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের শত্রু হলো, কংগ্রেস লীগ পরস্পরের শত্রু হলো। ব্রিটিশরা তার কূটনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের জোরে সেই পরিস্থিতিতে শত্রুর পরিবর্তে পরিণত হলো মধ্যস্থতাকারীতে! এমনকি কমিউনিস্টরা পর্যন্ত এ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে না দাঁড়িয়ে, সাংবিধানিক রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যেকার বিভেদের পরিবর্তে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের হাতে হাত বেঁধে দেওয়ার জন্য দাঁড়ালো। ১৯৪৪ সালে গান্ধী জিন্নাহ্ আলোচনা ব্যর্থ হয়ে ভেঙে যাওয়ার পর কমিউনিস্ট নেতা পি. সি. যোশী লিখেছিলেন তাঁর বই They Shall Meet Again। তারা স্বাধীনতার জন্য নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে, কংগ্রেস লীগের বলয়ের বাইরে থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করলো না।
ব্রিটিশের শোষণ নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে জনগণের মধ্যে ক্রোধ ও প্রতিরোধের শক্তি সৃষ্টি হচ্ছিলো। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের দেউলিয়া চরিত্রের কারণে ব্রিটিশকে সংগ্রামের প্রধান ও সরাসরি লক্ষ্যবস্তু করা হলো না। এর ফলে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঐক্যের সৃষ্টি না হয়ে, তার মধ্যে ভাঙন ধরে, বিভেদের বীজ অঙ্কুরিত হলো।
স্বাধীনতা সংগ্রামে যে মধ্যশ্রেণী ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল ও নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থার মাধ্যমে ও তাদের অধীনে চাকরীর ভিত্তিতে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভারতের যে পুঁজি মালিকরা কংগ্রেস লীগের ওপর প্রভাব বিস্তার করতো তারা গঠিত হয়েছিল ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তাদের ওপর নির্ভরশীল থেকে। সাম্রাজ্যবাদের সাথে তাদের আপোষের সম্পর্ক ছিল। ১৯২৫ সালেই স্ট্যালিন বলেছিলেন যে, ভারতের দেশীয় পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে আপোষ করেছিল। এই শ্রেণীগত কারণে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা মূল ভূমিকা পালন করেছিল তাদের কোন মেরুদণ্ড ছিল না।
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা প্রকৃতপক্ষে ভারতের জনগণের প্রতিনিধি ছিল না। তারা ছিল ভারতের বৃহৎ ভূমি মালিক জমিদার ও পুঁজি মালিকদের প্রতিনিধি। গান্ধী, নেহরু, প্যাটেলের ওপর বিড়লার মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব কোন গোপন ব্যাপার ছিল না। বিড়লা টাটা ইত্যাদির স্বার্থের চাহিদা মেটাতেই কংগ্রেস ভারত ও বাঙলা ভাগ করেছিল। ভূমি মালিক নবাব নাইটরা, আদমজী ইস্পাহানীরা ছিলেন জিন্নাহ্রর পছন্দের লোক। মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমান ভূমি মালিক জমিদার ও পুঁজি মালিকদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশের প্রতিনিধি হিসাবে দাবী করেছিল পাকিস্তান।
ভারতের আপোষকামী রাজনৈতিক নেতৃত্ব চীনের মুক্তি যুদ্ধের মত ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামকে তার নিজস্ব গতিতে বিকশিত হতে দেয় নি। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তুমুল ও কঠিন সংগ্রাম করলে সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই ঐক্য গড়ে ওঠে। অন্যথায় বিভেদের শর্ত তৈরী হয়। ভারতে তাই হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের সাথে আপোষ করে, সংসদীয় রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আটকে থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের তথাকথিত স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করার কারণেই ভারতে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিতে পেরেছিল এবং ব্রিটিশের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছিল তাদের প্রয়োজন ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের। ভারত ও বাঙলা ভাগ ছিল তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।
৬.১২.২০২২